সুমন সুবহান

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ কি কনভেনশনাল যুদ্ধ নাকি ইনসারজেন্সি অপারেশন? অনেকেরই এই বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার নয়। তবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে শুরুতেই জানতে হবে ইনসারজেন্সি এবং কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন কী?
ইনসারজেন্সি অপারেশন বলতে বোঝায় একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান, যা সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকার বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এটি মূলত গেরিলা যুদ্ধ বা ‘অসম যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। এই ধরনের অপারেশনে ছোট ও হালকা অস্ত্রধারী একটি দল বা সংগঠন একটি বড় ও সুসজ্জিত নিয়মিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। ইনসারজেন্সি অপারেশনের মূল বৈশিষ্ট্য—
অসম প্রকৃতি: এটি কোনো প্রচলিত যুদ্ধ নয়, যেখানে দুটি সমান শক্তিশালী সামরিক বাহিনী মুখোমুখি লড়াই করে। বরং এখানে বিদ্রোহীরা কৌশল, গতিশীলতা এবং জনসংখ্যার সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।
গেরিলা কৌশল: বিদ্রোহীরা সরাসরি লড়াই এড়িয়ে অতর্কিত হামলা, গুপ্তহত্যা, বোমা হামলা এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। তারা সাধারণত বেসামরিক জনগণের মধ্যে মিশে থাকে, যার ফলে তাদের শনাক্ত করা বেশ কঠিন।
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য: এই অপারেশনের প্রধান লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা, যেমন বিদ্যমান সরকারকে উৎখাত করা, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে স্বাধীন করা বা কোনো রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।
পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সফল ও বিফল ইনসারজেন্সি অপারেশনের উদাহরণ আছে। যেমন—
ভিয়েতনাম যুদ্ধ: উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক বাহিনী এবং ভিয়েত কং গেরিলারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও তাদের মিত্র মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। এটি একটি ক্লাসিক ইনসারজেন্সি অপারেশনের উদাহরণ।
আফগানিস্তানে সোভিয়েত যুদ্ধ: আফগান মুজাহিদরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তারা সোভিয়েতদের তুলনায় অনেক দুর্বল হলেও স্থানীয় জনগণের সমর্থন ও গেরিলা কৌশলের মাধ্যমে সফল হয়েছিল।
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন: ভারতের উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে আসছে।
এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান শান্তিবাহিনী, ইউপিডিএফ এবং কুকি-চিন আর্মির সশস্ত্র তৎপরতাও এ ধরনের অপারেশনের উদাহরণ।
এই ধরনের অপারেশন প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এতে সামরিক কৌশলের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন হলো ইনসারজেন্সি দমন করার জন্য কোনো সরকার বা সামরিক বাহিনীর গৃহীত সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ। ইনসারজেন্সি অপারেশনের বিপরীতে, এই ধরনের অপারেশনের লক্ষ্য শুধু বিদ্রোহীদের সামরিকভাবে পরাজিত করা নয়, বরং তাদের মূল সমর্থন ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে বৈধতা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের প্রধান লক্ষ্য হলো জনসংখ্যার সমর্থন জয় করা। এর কৌশলগুলো হলো—
সামরিক পন্থায় দমন: বিদ্রোহীদের সরাসরি সামরিক হামলা, নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে দুর্বল ও ধ্বংস করা।
জনসংখ্যার সুরক্ষা: সামরিক বাহিনী শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না, বরং স্থানীয় বেসামরিক জনগণকে বিদ্রোহীদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করে তাদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করে।
শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা: বিদ্রোহের মূল কারণগুলো, যেমন—অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক দুর্নীতি বা সামাজিক অন্যায়ের সমাধান করে সরকারের বৈধতা ও কার্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
তথ্যযুদ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক অভিযান: প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মন জয় করা এবং বিদ্রোহীদের আদর্শের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা।
পৃথিবীর ইতিহাসে বহু কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে কিছু সফল এবং কিছু বিফল হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—
মালয় জরুরি অবস্থা: ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বাহিনী মালয়ে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেছিল। তারা সামরিক অভিযানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের সমর্থন জয় করেছিল, যা সফল কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের উদাহরণ।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ: মার্কিন বাহিনী ভিয়েতনামে কাউন্টার ইনসারজেন্সি কৌশল ব্যবহার করলেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তারা পরাজিত হয়।
আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধ: আধুনিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এই দুই দেশে কাউন্টার ইনসারজেন্সি কৌশল প্রয়োগ করেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এবং জঙ্গিদের দমন করা। তবে এই অপারেশনগুলোর সাফল্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী, ইউপিডিএফ এবং কুকি-চিন আর্মির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপারেশন: শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন ছিল বাংলাদেশ সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী সামরিক ও অসামরিক কৌশল, যা ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেষ হয়। এই অপারেশনটি মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা ‘শান্তিবাহিনী’র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমানে কুকি-চিন সংগঠনের বিরুদ্ধে অনুরূপ অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে।
কাউন্টার ইনসারজেন্সি একটি অত্যন্ত জটিল অপারেশন প্রক্রিয়া, যা কেবল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং জনগণের চাহিদার গভীর বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল।
একটি সফল কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের মূল লক্ষ্য শুধু বিদ্রোহীদের সামরিকভাবে পরাজিত করা নয়, বরং জনগণের সমর্থন লাভ করা। কারণ বিদ্রোহীরা সাধারণত জনগণের মধ্যে মিশে থাকে এবং তাদের সমর্থন ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তাই এ ধরনের অপারেশনের কৌশল নিচের নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়—
জনগণকে সুরক্ষিত রাখা: এই অপারেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনগণকে বিদ্রোহীদের হুমকি থেকে রক্ষা করা। যদি জনগণ নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে, তবে তারা সরকারের ওপর আস্থা রাখবে এবং বিদ্রোহীদের সমর্থন থেকে বিরত থাকবে।
সরকারের বৈধতা প্রতিষ্ঠা: কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের একটি বড় অংশ হলো স্থানীয় জনগণের কাছে সরকারের শাসনকে বৈধ এবং উপকারী প্রমাণ করা। এর মধ্যে রয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক সেবা (যেমন বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্যসেবা) নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা।
বিদ্রোহীদের থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা: সামরিক এবং অসামরিক উভয় উপায়ে বিদ্রোহীদের তাদের সমর্থনকারী জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা হয়। এর মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিদ্রোহীদের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের সরবরাহের পথ বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত।
সামরিক এবং বেসামরিক সমন্বয়: এই ধরনের অপারেশনে সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং বেসামরিক সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে গভীর সমন্বয় প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, আর বেসামরিক সংস্থাগুলো জনসেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।
কনভেনশনাল যুদ্ধ হলো একধরনের সশস্ত্র সংঘাত, যা দুটি বা তার বেশি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সুসংগঠিত ও সুপ্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ধরনের যুদ্ধে সামরিক বাহিনী তাদের চিরাচরিত যুদ্ধাস্ত্র, যেমন—ট্যাংক, বিমান, যুদ্ধজাহাজ এবং কামান ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি লড়াই করে। কনভেনশনাল যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য—
রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সংঘাত: কনভেনশনাল যুদ্ধ সাধারণত দুটি দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যুদ্ধ। এখানে কোনো অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী বা বিদ্রোহী দল সরাসরি অংশ নেয় না।
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য: কনভেনশনাল যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো শত্রুপক্ষের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল বা ধ্বংস করে দেওয়া এবং তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেওয়া। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামরিক উদ্দেশ্য (যেমন—শত্রু দেশের ভূখণ্ড দখল, সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো ইত্যাদি) অর্জন করা হয়।
চিরাচরিত যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার: কনভেনশনাল যুদ্ধে রাসায়নিক, জীবাণু বা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অপ্রচলিত অস্ত্র ব্যবহার করা হয় না। বরং সামরিক বাহিনী তাদের নিয়মিত অস্ত্র ও কৌশল (যেমন—আক্রমণ, প্রতিরক্ষা, পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি) ব্যবহার করে।
যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়মকানুন: কনভেনশনাল যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন, যেমন—জেনেভা কনভেনশনের মতো চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক জনগণের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, তা নির্ধারণ করে।
ইতিহাসের অনেক বড় বড় যুদ্ধই কনভেনশনাল যুদ্ধের উদাহরণ। যেমন—
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং ধ্বংসাত্মক এই যুদ্ধগুলো ছিল মূলত কনভেনশনাল যুদ্ধ, যেখানে বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীগুলো ব্যাপক অস্ত্র ও সেনাসজ্জা নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়েছিল।
উপসাগরীয় যুদ্ধ: ইরাকের কুয়েত দখল করার পর আমেরিকার নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক জোটের সঙ্গে ইরাকের সামরিক বাহিনীর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা একটি ক্লাসিক কনভেনশনাল যুদ্ধের উদাহরণ। এখানে দুই পক্ষের সুসংগঠিত বাহিনী খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি লড়াই করেছিল।
ইরান-ইরাক যুদ্ধ: এটিও দুটি দেশের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কনভেনশনাল যুদ্ধ ছিল। এ ছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরায়েল-ইরান, কিছুদিন আগে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান—এরকম অসংখ্য প্রচলিত যুদ্ধের উদাহরণ দেওয়া যাবে।
ইনসারজেন্সি অপারেশন এবং কনভেনশনাল যুদ্ধের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কনভেনশনাল যুদ্ধ হয় দুটি বা তার বেশি রাষ্ট্রের সুসংগঠিত সামরিক বাহিনীর মধ্যে, যেখানে ইনসারজেন্সি অপারেশন হলো একটি দুর্বল, অরাষ্ট্রীয় দল কর্তৃক একটি শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসম যুদ্ধ। নিচে এই দুই প্রকার যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হলো।
অংশগ্রহণকারী পক্ষ: ইনসারজেন্সি অপারেশনে একটি অরাষ্ট্রীয় বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী বনাম একটি রাষ্ট্রীয় সরকার। কনভেনশনাল যুদ্ধ দুটি বা তার বেশি রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়।
যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃতি: ইনসারজেন্সি অপারেশনে কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র নেই। বিদ্রোহীরা সাধারণত বেসামরিক জনগণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে। কনভেনশনাল যুদ্ধে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র বা সম্মুখসমর, যেমন মরুভূমি, সাগর বা সীমান্ত এলাকা।
রণকৌশল: ইনসারজেন্সি অপারেশন অসম যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন মাইনর অপারেশন, যেমন—রেইড, অ্যাম্বুশ, হাইডআউট ইত্যাদি রণকৌশলের মাধ্যমে অতর্কিত হামলা, গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধ ‘প্রতিসম যুদ্ধ’ হিসেবে পরিচিত। এতে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, নৌজাহাজ ও পদাতিক বাহিনীর মতো বড় সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিভিন্ন মেজর অপারেশন, যেমন—ডিফেন্স, অ্যাটাক, টিআরডি, অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট, পারস্যু ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি লড়াই করা হয়।
যুদ্ধাস্ত্র: ইনসারজেন্সি অপারেশনে হালকা অস্ত্র, বিস্ফোরক, ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস এবং ছোট আকারের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে ভারী সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র, যেমন ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, নৌবহর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
যুদ্ধকালীন সময়সীমা: ইনসারজেন্সি অপারেশন সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এতে সামরিক বিজয়ের পরিবর্তে অনেক সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধ তুলনামূলকভাবে কম সময়ের জন্য সংঘটিত হয়, যেখানে দ্রুত ও চূড়ান্ত সামরিক বিজয় লক্ষ্য থাকে।
বেসামরিক জনগণের ভূমিকা: ইনসারজেন্সি অপারেশনে বেসামরিক জনগণ প্রায়শই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে এবং উভয় পক্ষের সমর্থন লাভের জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে বেসামরিক জনগণের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম থাকে, যদিও তারা যুদ্ধের পরোক্ষ শিকার হতে পারে।
লক্ষ্যবস্তু: ইনসারজেন্সি অপারেশনে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা, সরকারি স্থাপনা এবং বেসামরিক জনগণকেও লক্ষ্য করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে প্রধানত সামরিক স্থাপনা ও শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ করা হয়।
আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু থেকে এবং এর বেশির ভাগ সময়জুড়ে পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন বলা হতো। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে—
বিদ্রোহ দমন: পাকিস্তান সরকার এটাকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ দমনের একটি সামরিক অভিযান হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তারা অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।
গেরিলা যুদ্ধ: বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী প্রাথমিকভাবে প্রচলিত সামরিক শক্তির অভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে। এটি কাউন্টার ইনসারজেন্সির একটি মূল বৈশিষ্ট্য, যেখানে একটি ছোট, অনিয়মিত বাহিনী একটি বড়, নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে।
জনগণের সমর্থন: মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের সমর্থন নিয়েই যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তারা জনগণের মধ্যে মিশে থেকে অতর্কিত হামলা চালাতেন। পাকিস্তানি বাহিনী চেষ্টা করেছিল জনগণের থেকে এই সমর্থন বিচ্ছিন্ন করতে, যা একটি কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কেবল একটি একক ধরনের যুদ্ধ ছিল না এবং এটি ইনসারজেন্সি অপারেশন নাকি কনভেনশনাল যুদ্ধ, এভাবে সরাসরি যতিচিহ্ন টানা যাবে না। কারণ এটি ইনসারজেন্সি বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হয়ে, জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর (ভারত ও মুক্তিবাহিনী) প্রচলিত সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ একই সঙ্গে কনভেনশনাল যুদ্ধ এবং কাউন্টার ইনসারজেন্সি উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এটি আসলে উভয় ধরনের যুদ্ধের এক জটিল মিশ্রণ, যা শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস ‘অপারেশন সার্চলাইট’ দিয়ে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের জটিল রণকৌশল একাধিক ধাপ ও কৌশলের সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছিল।
স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাথমিক ধাপ (মার্চ-নভেম্বর ১৯৭১): এই ধাপে ইনসারজেন্সি অপারেশন ও গেরিলা যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তান আর্মির ক্ষতিসাধন এবং সৈন্যদের মনোবল দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য ছিল—
অসম লড়াই: যুদ্ধের শুরুতে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তুলনায় সামরিক শক্তিতে দুর্বল ছিল। তাই তারা প্রচলিত সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে গেরিলা কৌশলকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়।
গেরিলা কৌশল: মুক্তিবাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা, অ্যাম্বুশ, যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া (যেমন—‘অপারেশন জ্যাকপট’-এর মাধ্যমে নৌপথ বন্ধ করা) এবং সামরিক স্থাপনায় নাশকতার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করে।
জনগণের সমর্থন: ইনসারজেন্সির মূল ভিত্তি হলো জনগণের সমর্থন। মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে মিশে থেকে তাদের কাছ থেকে খাদ্য, আশ্রয়, তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করত, যা তাদের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য ছিল।
স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত ধাপ (ডিসেম্বর ১৯৭১): এই ধাপে কনভেনশনাল যুদ্ধ পরিচালিত হয়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে মিত্রবাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—
ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ: ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। এর ফলে যুদ্ধটি প্রচলিত সামরিক সংঘাতের রূপ ধারণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই সময় প্রচলিত সামরিক কৌশল, যেমন—সম্মুখযুদ্ধ, ট্যাংক যুদ্ধ, বিমান হামলা (যেমন—বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অপারেশন) এবং নৌ-অভিযান (যেমন—অপারেশন জ্যাকপট) পরিচালিত হয়েছিল।
যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম: ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত দলগুলো একত্রিত হয়ে প্রচলিত সামরিক কৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তানি বাহিনীর সুসংগঠিত ঘাঁটির ওপর আক্রমণ শুরু করে। এই সময়ে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান এবং নৌবাহিনীর মতো ভারী সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।
দ্রুত বিজয়: এই প্রচলিত যুদ্ধের কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর পতন দ্রুত হয় এবং মাত্র ১৩ দিনের মধ্যেই ঢাকা দখল ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়।
২.
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওরব্যাট (Order of Battle)-এ মূলত ৩টি পদাতিক ডিভিশন ছিল। নবম পদাতিক ডিভিশন (১০৭ ব্রিগেড, ৫৭ ব্রিগেড ও ৪৮ ব্রিগেড), ১৪তম পদাতিক ডিভিশন (৫৩ ব্রিগেড, ২০২ ব্রিগেড ও ২৭ ব্রিগেড) এবং ১৬তম পদাতিক ডিভিশন (২৩ ব্রিগেড, ২০৫ ব্রিগেড ও ৩৪ ব্রিগেড)। যুদ্ধের শেষ দিকে আরও ২টি অ্যাডহক ডিভিশন গঠন করা হয়েছিল, ৩৬ অ্যাডহক ডিভিশন এবং ৩৯ অ্যাডহক ডিভিশন, তবে এদের ক্ষমতা সীমিত ছিল। এ ছাড়া রাজাকার, আলবদর, আলশামস, ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেসের সমন্বয়ে প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং নৌবাহিনীর কয়েকটি গানবোট ও বিমানবাহিনীর সামান্য সংখ্যক বিমান ছিল।
সব মিলিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৯৩ হাজার, যার মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৫৪ হাজার, অন্যান্য সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর (যেমন—পাকিস্তান রেঞ্জার্স, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্য) প্রায় ৩৩ হাজার এবং অসামরিক ব্যক্তি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রায় ৬ হাজার।
লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি জানতেন, তার এই সীমিত সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধরসদ প্রতিপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় বা শক্তিতে অনেক দুর্বল। তাই তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে রণকৌশল ব্যবহার করেন, তাকে সামরিক কৌশলগত পরিভাষায় ‘ফরট্রেস কনসেপ্ট’ বলে।
ফরট্রেস কনসেপ্ট বা ‘দুর্গ ধারণা’ একটি প্রাচীন সামরিক কৌশল, যা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি এমন একটি প্রতিরক্ষা কৌশল, যেখানে কোনো সামরিক বাহিনী কিছু নির্দিষ্ট এলাকাকে দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে চায়। তিনি সীমান্ত শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে দুর্ভেদ্য দুর্গে (যেমন—যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ভৈরব বাজার ইত্যাদি) পরিণত করেন। এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত করা, দুর্গের মতো সুরক্ষিত অবস্থান থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার গতিবিধি ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এবং একটি সুরক্ষিত স্থানে থেকে তার সীমিত সংখ্যক সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করা। নিয়াজির এই কৌশলের বিপরীতে মিত্রবাহিনী নিয়েছিল বাইপাস পলিসি, অর্থাৎ দুর্গগুলোকে এড়িয়ে বা বিচ্ছিন্ন করে দ্রুত ঢাকায় পৌঁছানো।
৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ব্যবস্থাপকের বাংলোতে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাথমিক সামরিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এই সভায় কর্নেল এম এ জি ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়াউর রহমানসহ তৎকালীন ২৭ জন ঊর্ধ্বতন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই বাংলাদেশকে চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কর্নেল ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।
১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিবাহিনী ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ ফোর্সেস নামে নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ১১-১৭ জুলাই ১৯৭১ তারিখে কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ ফোর্সেস সদর দপ্তরে (মুক্তিবাহিনীর প্রধান কার্যালয়) অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারস সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ এবং নিয়মিত বাহিনীর প্রয়োজনে ব্রিগেড (জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স) গঠন করা হয়। এভাবেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটা নিয়মিত বাহিনীর রূপ নেয় এবং এই বাহিনীর মূল ভিত্তি ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। সব মিলিয়ে এই বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার। এ ছাড়া গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী ছিল প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ বা তারও বেশি। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধার মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১ লাখ ৮০ হাজার থেকে ২ লাখ পর্যন্ত।
আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অপারেশন জ্যাকপট, ব্যাটল অব শিরোমণি, ব্যাটল অব কামালপুর, ব্যাটল অব হিলি, ব্যাটল অব বেলোনিয়া বালজ আমাদের সামরিক ইতিহাসের অংশ এবং গর্বের বিষয়।
ব্যাটল অব বেলোনিয়া বালজ: ১০ নভেম্বর ১৯৭১ সালে ‘ব্যাটল অব বেলোনিয়া বালজ’-এ পাকিস্তানি বাহিনীর একজন মেজরসহ ৭২ জন সৈনিক আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে ১০ ইস্ট বেঙ্গল এবং ভারতীয় বাহিনী শত্রুপক্ষের মূল অবস্থান এড়িয়ে গোপনে তাদের পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এটি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য একটি বড় নৈতিক পরাজয় এবং মুক্তিবাহিনীর জন্য একটি বড় বিজয়। এই যুদ্ধের সফল সামরিক কৌশল বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিসহ বিভিন্ন দেশের সামরিক স্কুলে উদাহরণ হিসেবে পড়ানো হয়।
ব্যাটল অব হিলি: হিলির যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মুখযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গনে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধগুলোর একটি ‘ব্যাটল অব হিলি’ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের হাতে গোনা কয়েকটি সুসংগঠিত এবং কনভেনশনাল যুদ্ধের অন্যতম। অসংখ্য কংক্রিট বাঙ্কার এবং মাইনফিল্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী এখানে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যার ফলে মিত্রবাহিনী এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। এই যুদ্ধ মূলত দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। এর প্রথম পর্ব ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর ১৯৭১ এবং দ্বিতীয় পর্ব ১০ থেকে ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ দুই পর্বে প্রায় ২০ দিন ধরে হিলিতে যুদ্ধ চলে। এই দুই পর্বের যুদ্ধের মাধ্যমে হিলি মুক্ত হয় এবং মিত্রবাহিনী বগুড়ার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হিলির যুদ্ধে মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী উভয়ই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত প্রতিরোধের কারণে উভয় পক্ষেই ব্যাপক হতাহত হয়েছিল।
ব্যাটল অব কামালপুর: ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর কামালপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত সুরক্ষিত ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটির পতন ঘটে। তারা এখানে বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ এবং মাইনফিল্ড তৈরি করে এটিকে একটি দুর্গে পরিণত করেছিল। এই ঘাঁটির পতন মানে ছিল ময়মনসিংহ ও ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাওয়া। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী একত্রে এই ঘাঁটিটি দীর্ঘ ২২ দিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধ ‘ব্যাটল অব কামালপুর’ নামে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধারা এই ঘাঁটি দখলের জন্য বেশ কয়েকবার আক্রমণ চালান। এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১৮টি ছোট-বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষই ব্যাপক হতাহতের শিকার হয়। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজের মতো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের অসম সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ কামালপুরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি বীরত্ব ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে।
অপারেশন ক্যাকটাস লিলি: ১৯৭১ সালের ৯-১২ ডিসেম্বর তারিখে মিত্রবাহিনী মেঘনা নদী পার হওয়ার জন্য একটি সাহসী হেলিকপ্টারভিত্তিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যা ‘অপারেশন ক্যাকটাস লিলি’ বা ‘মেঘনা হেলি ব্রিজ’ নামে পরিচিত। পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান বাধাগ্রস্ত করার জন্য আশুগঞ্জের ভৈরব সেতু ধ্বংস করেছিল। কিন্তু উক্ত তারিখে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এমআই-৪ হেলিকপ্টার ব্যবহার করে প্রায় ১১০টি সর্টির মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আইভি কোর এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মেঘনার পূর্ব পাড় থেকে রায়পুরা (নরসিংদী) এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। এটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সফল ও গুরুত্বপূর্ণ ‘রিভার ক্রসিং’ অপারেশন।
ভার্টিকাল এনভেলপমেন্ট: ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে টাঙ্গাইল এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারাশুট রেজিমেন্টের ২য় প্যারা ব্যাটালিয়নের প্রায় ৭০০ জন প্যারাট্রুপারকে নামানো হয়েছিল। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পরিচালিত সবচেয়ে বড় এয়ারবোর্ন অপারেশনগুলোর মধ্যে একটি। সামরিক ভাষায় এটি ‘ভার্টিকাল এনভেলপমেন্ট’ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যমুনা নদীর ওপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ পুংলি ব্রিজটি দখল করা। এই অপারেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩তম ব্রিগেডকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কাদের সিদ্দিকীর ‘কাদেরিয়া বাহিনী’র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযান পরিচালনার আগে কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ল্যান্ডিং জোনের স্থান নির্ধারণ করেন। এই অভিযানে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ এবং ল্যান্ডিং জোনের নিরাপত্তার জন্য ওই এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীকে ব্যস্ত রাখা, রোড ব্লক বসিয়ে পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং স্থলপথে সমন্বয় করা।
ব্যাটল অব শিরোমণি: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে খুলনার শিরোমণিতে সংঘটিত ‘ব্যাটল অব শিরোমণি’ একটি বিশেষ কৌশলগত ট্যাংক যুদ্ধ, যা সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিরল উদাহরণ। শিরোমণির এই যুদ্ধটি ভারত, পোল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ৩৫টি দেশের সামরিক প্রতিরক্ষা কলেজে পড়ানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি এমন একটি বিরল যুদ্ধ, যেখানে একই সঙ্গে ট্যাংক, আর্টিলারি, পদাতিক ও হাতাহাতি যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল।
৩.
যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্রেফ গৃহযুদ্ধ কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা অথবা ইনসারজেন্সি অপারেশন বলে চিহ্নিত করতে চান, তারা আসলে বেইমান এবং অজ্ঞ। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ কিশোর মুক্তিযোদ্ধা লালু, নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, মুক্তিযোদ্ধা ইউকে চিং মারমা, ক্র্যাক প্লাটুনের বদি, রুমি, খোকা, আলতাফ মাহমুদ, আবুল বারাক আলভী, লিনু বিল্লাহ, দিনু বিল্লাহ, নুহে আলম বিল্লাহ, খাইরুল আলম, আজম খান, ইমতিয়াজ বুলবুলের রক্ত-ঘামস্নাত স্বাধীনতাযুদ্ধ। স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের আবেগের জায়গা।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ কি কনভেনশনাল যুদ্ধ নাকি ইনসারজেন্সি অপারেশন? অনেকেরই এই বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার নয়। তবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে শুরুতেই জানতে হবে ইনসারজেন্সি এবং কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন কী?
ইনসারজেন্সি অপারেশন বলতে বোঝায় একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান, যা সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকার বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এটি মূলত গেরিলা যুদ্ধ বা ‘অসম যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। এই ধরনের অপারেশনে ছোট ও হালকা অস্ত্রধারী একটি দল বা সংগঠন একটি বড় ও সুসজ্জিত নিয়মিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। ইনসারজেন্সি অপারেশনের মূল বৈশিষ্ট্য—
অসম প্রকৃতি: এটি কোনো প্রচলিত যুদ্ধ নয়, যেখানে দুটি সমান শক্তিশালী সামরিক বাহিনী মুখোমুখি লড়াই করে। বরং এখানে বিদ্রোহীরা কৌশল, গতিশীলতা এবং জনসংখ্যার সমর্থনের ওপর নির্ভর করে।
গেরিলা কৌশল: বিদ্রোহীরা সরাসরি লড়াই এড়িয়ে অতর্কিত হামলা, গুপ্তহত্যা, বোমা হামলা এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। তারা সাধারণত বেসামরিক জনগণের মধ্যে মিশে থাকে, যার ফলে তাদের শনাক্ত করা বেশ কঠিন।
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য: এই অপারেশনের প্রধান লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা, যেমন বিদ্যমান সরকারকে উৎখাত করা, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে স্বাধীন করা বা কোনো রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।
পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সফল ও বিফল ইনসারজেন্সি অপারেশনের উদাহরণ আছে। যেমন—
ভিয়েতনাম যুদ্ধ: উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক বাহিনী এবং ভিয়েত কং গেরিলারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও তাদের মিত্র মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। এটি একটি ক্লাসিক ইনসারজেন্সি অপারেশনের উদাহরণ।
আফগানিস্তানে সোভিয়েত যুদ্ধ: আফগান মুজাহিদরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তারা সোভিয়েতদের তুলনায় অনেক দুর্বল হলেও স্থানীয় জনগণের সমর্থন ও গেরিলা কৌশলের মাধ্যমে সফল হয়েছিল।
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন: ভারতের উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে আসছে।
এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান শান্তিবাহিনী, ইউপিডিএফ এবং কুকি-চিন আর্মির সশস্ত্র তৎপরতাও এ ধরনের অপারেশনের উদাহরণ।
এই ধরনের অপারেশন প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এতে সামরিক কৌশলের পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন হলো ইনসারজেন্সি দমন করার জন্য কোনো সরকার বা সামরিক বাহিনীর গৃহীত সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ। ইনসারজেন্সি অপারেশনের বিপরীতে, এই ধরনের অপারেশনের লক্ষ্য শুধু বিদ্রোহীদের সামরিকভাবে পরাজিত করা নয়, বরং তাদের মূল সমর্থন ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে বৈধতা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের প্রধান লক্ষ্য হলো জনসংখ্যার সমর্থন জয় করা। এর কৌশলগুলো হলো—
সামরিক পন্থায় দমন: বিদ্রোহীদের সরাসরি সামরিক হামলা, নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে দুর্বল ও ধ্বংস করা।
জনসংখ্যার সুরক্ষা: সামরিক বাহিনী শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না, বরং স্থানীয় বেসামরিক জনগণকে বিদ্রোহীদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করে তাদের আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করে।
শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা: বিদ্রোহের মূল কারণগুলো, যেমন—অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক দুর্নীতি বা সামাজিক অন্যায়ের সমাধান করে সরকারের বৈধতা ও কার্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
তথ্যযুদ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক অভিযান: প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের মন জয় করা এবং বিদ্রোহীদের আদর্শের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা।
পৃথিবীর ইতিহাসে বহু কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে কিছু সফল এবং কিছু বিফল হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—
মালয় জরুরি অবস্থা: ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বাহিনী মালয়ে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেছিল। তারা সামরিক অভিযানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের সমর্থন জয় করেছিল, যা সফল কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের উদাহরণ।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ: মার্কিন বাহিনী ভিয়েতনামে কাউন্টার ইনসারজেন্সি কৌশল ব্যবহার করলেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তারা পরাজিত হয়।
আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধ: আধুনিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এই দুই দেশে কাউন্টার ইনসারজেন্সি কৌশল প্রয়োগ করেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা এবং জঙ্গিদের দমন করা। তবে এই অপারেশনগুলোর সাফল্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী, ইউপিডিএফ এবং কুকি-চিন আর্মির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপারেশন: শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন ছিল বাংলাদেশ সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী সামরিক ও অসামরিক কৌশল, যা ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়ে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেষ হয়। এই অপারেশনটি মূলত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা ‘শান্তিবাহিনী’র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। বর্তমানে কুকি-চিন সংগঠনের বিরুদ্ধে অনুরূপ অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে।
কাউন্টার ইনসারজেন্সি একটি অত্যন্ত জটিল অপারেশন প্রক্রিয়া, যা কেবল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না, বরং স্থানীয় সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং জনগণের চাহিদার গভীর বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল।
একটি সফল কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের মূল লক্ষ্য শুধু বিদ্রোহীদের সামরিকভাবে পরাজিত করা নয়, বরং জনগণের সমর্থন লাভ করা। কারণ বিদ্রোহীরা সাধারণত জনগণের মধ্যে মিশে থাকে এবং তাদের সমর্থন ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তাই এ ধরনের অপারেশনের কৌশল নিচের নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়—
জনগণকে সুরক্ষিত রাখা: এই অপারেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনগণকে বিদ্রোহীদের হুমকি থেকে রক্ষা করা। যদি জনগণ নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে, তবে তারা সরকারের ওপর আস্থা রাখবে এবং বিদ্রোহীদের সমর্থন থেকে বিরত থাকবে।
সরকারের বৈধতা প্রতিষ্ঠা: কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের একটি বড় অংশ হলো স্থানীয় জনগণের কাছে সরকারের শাসনকে বৈধ এবং উপকারী প্রমাণ করা। এর মধ্যে রয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক সেবা (যেমন বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্যসেবা) নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা।
বিদ্রোহীদের থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা: সামরিক এবং অসামরিক উভয় উপায়ে বিদ্রোহীদের তাদের সমর্থনকারী জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা হয়। এর মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিদ্রোহীদের যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের সরবরাহের পথ বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত।
সামরিক এবং বেসামরিক সমন্বয়: এই ধরনের অপারেশনে সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং বেসামরিক সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে গভীর সমন্বয় প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, আর বেসামরিক সংস্থাগুলো জনসেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।
কনভেনশনাল যুদ্ধ হলো একধরনের সশস্ত্র সংঘাত, যা দুটি বা তার বেশি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সুসংগঠিত ও সুপ্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ধরনের যুদ্ধে সামরিক বাহিনী তাদের চিরাচরিত যুদ্ধাস্ত্র, যেমন—ট্যাংক, বিমান, যুদ্ধজাহাজ এবং কামান ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি লড়াই করে। কনভেনশনাল যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য—
রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সংঘাত: কনভেনশনাল যুদ্ধ সাধারণত দুটি দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যুদ্ধ। এখানে কোনো অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী বা বিদ্রোহী দল সরাসরি অংশ নেয় না।
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য: কনভেনশনাল যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো শত্রুপক্ষের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল বা ধ্বংস করে দেওয়া এবং তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেওয়া। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামরিক উদ্দেশ্য (যেমন—শত্রু দেশের ভূখণ্ড দখল, সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো ইত্যাদি) অর্জন করা হয়।
চিরাচরিত যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার: কনভেনশনাল যুদ্ধে রাসায়নিক, জীবাণু বা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অপ্রচলিত অস্ত্র ব্যবহার করা হয় না। বরং সামরিক বাহিনী তাদের নিয়মিত অস্ত্র ও কৌশল (যেমন—আক্রমণ, প্রতিরক্ষা, পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি) ব্যবহার করে।
যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়মকানুন: কনভেনশনাল যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন, যেমন—জেনেভা কনভেনশনের মতো চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, যা যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক জনগণের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, তা নির্ধারণ করে।
ইতিহাসের অনেক বড় বড় যুদ্ধই কনভেনশনাল যুদ্ধের উদাহরণ। যেমন—
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং ধ্বংসাত্মক এই যুদ্ধগুলো ছিল মূলত কনভেনশনাল যুদ্ধ, যেখানে বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীগুলো ব্যাপক অস্ত্র ও সেনাসজ্জা নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়েছিল।
উপসাগরীয় যুদ্ধ: ইরাকের কুয়েত দখল করার পর আমেরিকার নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক জোটের সঙ্গে ইরাকের সামরিক বাহিনীর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা একটি ক্লাসিক কনভেনশনাল যুদ্ধের উদাহরণ। এখানে দুই পক্ষের সুসংগঠিত বাহিনী খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি লড়াই করেছিল।
ইরান-ইরাক যুদ্ধ: এটিও দুটি দেশের নিয়মিত সামরিক বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কনভেনশনাল যুদ্ধ ছিল। এ ছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন, ইসরায়েল-ইরান, কিছুদিন আগে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান—এরকম অসংখ্য প্রচলিত যুদ্ধের উদাহরণ দেওয়া যাবে।
ইনসারজেন্সি অপারেশন এবং কনভেনশনাল যুদ্ধের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। কনভেনশনাল যুদ্ধ হয় দুটি বা তার বেশি রাষ্ট্রের সুসংগঠিত সামরিক বাহিনীর মধ্যে, যেখানে ইনসারজেন্সি অপারেশন হলো একটি দুর্বল, অরাষ্ট্রীয় দল কর্তৃক একটি শক্তিশালী সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসম যুদ্ধ। নিচে এই দুই প্রকার যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হলো।
অংশগ্রহণকারী পক্ষ: ইনসারজেন্সি অপারেশনে একটি অরাষ্ট্রীয় বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী বনাম একটি রাষ্ট্রীয় সরকার। কনভেনশনাল যুদ্ধ দুটি বা তার বেশি রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত হয়।
যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃতি: ইনসারজেন্সি অপারেশনে কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র নেই। বিদ্রোহীরা সাধারণত বেসামরিক জনগণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে। কনভেনশনাল যুদ্ধে সুনির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র বা সম্মুখসমর, যেমন মরুভূমি, সাগর বা সীমান্ত এলাকা।
রণকৌশল: ইনসারজেন্সি অপারেশন অসম যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন মাইনর অপারেশন, যেমন—রেইড, অ্যাম্বুশ, হাইডআউট ইত্যাদি রণকৌশলের মাধ্যমে অতর্কিত হামলা, গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধ ‘প্রতিসম যুদ্ধ’ হিসেবে পরিচিত। এতে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, নৌজাহাজ ও পদাতিক বাহিনীর মতো বড় সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিভিন্ন মেজর অপারেশন, যেমন—ডিফেন্স, অ্যাটাক, টিআরডি, অ্যাডভান্স টু কন্টাক্ট, পারস্যু ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি লড়াই করা হয়।
যুদ্ধাস্ত্র: ইনসারজেন্সি অপারেশনে হালকা অস্ত্র, বিস্ফোরক, ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস এবং ছোট আকারের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে ভারী সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্র, যেমন ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, নৌবহর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
যুদ্ধকালীন সময়সীমা: ইনসারজেন্সি অপারেশন সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এতে সামরিক বিজয়ের পরিবর্তে অনেক সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধ তুলনামূলকভাবে কম সময়ের জন্য সংঘটিত হয়, যেখানে দ্রুত ও চূড়ান্ত সামরিক বিজয় লক্ষ্য থাকে।
বেসামরিক জনগণের ভূমিকা: ইনসারজেন্সি অপারেশনে বেসামরিক জনগণ প্রায়শই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে এবং উভয় পক্ষের সমর্থন লাভের জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে বেসামরিক জনগণের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম থাকে, যদিও তারা যুদ্ধের পরোক্ষ শিকার হতে পারে।
লক্ষ্যবস্তু: ইনসারজেন্সি অপারেশনে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা, সরকারি স্থাপনা এবং বেসামরিক জনগণকেও লক্ষ্য করা হয়। কনভেনশনাল যুদ্ধে প্রধানত সামরিক স্থাপনা ও শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ করা হয়।
আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু থেকে এবং এর বেশির ভাগ সময়জুড়ে পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন বলা হতো। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে—
বিদ্রোহ দমন: পাকিস্তান সরকার এটাকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ দমনের একটি সামরিক অভিযান হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তারা অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।
গেরিলা যুদ্ধ: বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী প্রাথমিকভাবে প্রচলিত সামরিক শক্তির অভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে। এটি কাউন্টার ইনসারজেন্সির একটি মূল বৈশিষ্ট্য, যেখানে একটি ছোট, অনিয়মিত বাহিনী একটি বড়, নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে।
জনগণের সমর্থন: মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের সমর্থন নিয়েই যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তারা জনগণের মধ্যে মিশে থেকে অতর্কিত হামলা চালাতেন। পাকিস্তানি বাহিনী চেষ্টা করেছিল জনগণের থেকে এই সমর্থন বিচ্ছিন্ন করতে, যা একটি কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কেবল একটি একক ধরনের যুদ্ধ ছিল না এবং এটি ইনসারজেন্সি অপারেশন নাকি কনভেনশনাল যুদ্ধ, এভাবে সরাসরি যতিচিহ্ন টানা যাবে না। কারণ এটি ইনসারজেন্সি বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হয়ে, জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মিত্রবাহিনীর (ভারত ও মুক্তিবাহিনী) প্রচলিত সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ একই সঙ্গে কনভেনশনাল যুদ্ধ এবং কাউন্টার ইনসারজেন্সি উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এটি আসলে উভয় ধরনের যুদ্ধের এক জটিল মিশ্রণ, যা শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস ‘অপারেশন সার্চলাইট’ দিয়ে। আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের জটিল রণকৌশল একাধিক ধাপ ও কৌশলের সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছিল।
স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাথমিক ধাপ (মার্চ-নভেম্বর ১৯৭১): এই ধাপে ইনসারজেন্সি অপারেশন ও গেরিলা যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তান আর্মির ক্ষতিসাধন এবং সৈন্যদের মনোবল দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য ছিল—
অসম লড়াই: যুদ্ধের শুরুতে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তুলনায় সামরিক শক্তিতে দুর্বল ছিল। তাই তারা প্রচলিত সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে গেরিলা কৌশলকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়।
গেরিলা কৌশল: মুক্তিবাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা, অ্যাম্বুশ, যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া (যেমন—‘অপারেশন জ্যাকপট’-এর মাধ্যমে নৌপথ বন্ধ করা) এবং সামরিক স্থাপনায় নাশকতার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করে।
জনগণের সমর্থন: ইনসারজেন্সির মূল ভিত্তি হলো জনগণের সমর্থন। মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনগণের মধ্যে মিশে থেকে তাদের কাছ থেকে খাদ্য, আশ্রয়, তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভ করত, যা তাদের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য ছিল।
স্বাধীনতাযুদ্ধের চূড়ান্ত ধাপ (ডিসেম্বর ১৯৭১): এই ধাপে কনভেনশনাল যুদ্ধ পরিচালিত হয়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে মিত্রবাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—
ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ: ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। এর ফলে যুদ্ধটি প্রচলিত সামরিক সংঘাতের রূপ ধারণ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই সময় প্রচলিত সামরিক কৌশল, যেমন—সম্মুখযুদ্ধ, ট্যাংক যুদ্ধ, বিমান হামলা (যেমন—বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অপারেশন) এবং নৌ-অভিযান (যেমন—অপারেশন জ্যাকপট) পরিচালিত হয়েছিল।
যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম: ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত দলগুলো একত্রিত হয়ে প্রচলিত সামরিক কৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তানি বাহিনীর সুসংগঠিত ঘাঁটির ওপর আক্রমণ শুরু করে। এই সময়ে ট্যাংক, যুদ্ধবিমান এবং নৌবাহিনীর মতো ভারী সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।
দ্রুত বিজয়: এই প্রচলিত যুদ্ধের কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর পতন দ্রুত হয় এবং মাত্র ১৩ দিনের মধ্যেই ঢাকা দখল ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়।
২.
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওরব্যাট (Order of Battle)-এ মূলত ৩টি পদাতিক ডিভিশন ছিল। নবম পদাতিক ডিভিশন (১০৭ ব্রিগেড, ৫৭ ব্রিগেড ও ৪৮ ব্রিগেড), ১৪তম পদাতিক ডিভিশন (৫৩ ব্রিগেড, ২০২ ব্রিগেড ও ২৭ ব্রিগেড) এবং ১৬তম পদাতিক ডিভিশন (২৩ ব্রিগেড, ২০৫ ব্রিগেড ও ৩৪ ব্রিগেড)। যুদ্ধের শেষ দিকে আরও ২টি অ্যাডহক ডিভিশন গঠন করা হয়েছিল, ৩৬ অ্যাডহক ডিভিশন এবং ৩৯ অ্যাডহক ডিভিশন, তবে এদের ক্ষমতা সীমিত ছিল। এ ছাড়া রাজাকার, আলবদর, আলশামস, ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেসের সমন্বয়ে প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং নৌবাহিনীর কয়েকটি গানবোট ও বিমানবাহিনীর সামান্য সংখ্যক বিমান ছিল।
সব মিলিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৯৩ হাজার, যার মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৫৪ হাজার, অন্যান্য সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর (যেমন—পাকিস্তান রেঞ্জার্স, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্য) প্রায় ৩৩ হাজার এবং অসামরিক ব্যক্তি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রায় ৬ হাজার।
লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি জানতেন, তার এই সীমিত সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধরসদ প্রতিপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় বা শক্তিতে অনেক দুর্বল। তাই তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে রণকৌশল ব্যবহার করেন, তাকে সামরিক কৌশলগত পরিভাষায় ‘ফরট্রেস কনসেপ্ট’ বলে।
ফরট্রেস কনসেপ্ট বা ‘দুর্গ ধারণা’ একটি প্রাচীন সামরিক কৌশল, যা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি এমন একটি প্রতিরক্ষা কৌশল, যেখানে কোনো সামরিক বাহিনী কিছু নির্দিষ্ট এলাকাকে দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে চায়। তিনি সীমান্ত শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে দুর্ভেদ্য দুর্গে (যেমন—যশোর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, ভৈরব বাজার ইত্যাদি) পরিণত করেন। এই কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত করা, দুর্গের মতো সুরক্ষিত অবস্থান থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার গতিবিধি ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা এবং একটি সুরক্ষিত স্থানে থেকে তার সীমিত সংখ্যক সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করা। নিয়াজির এই কৌশলের বিপরীতে মিত্রবাহিনী নিয়েছিল বাইপাস পলিসি, অর্থাৎ দুর্গগুলোকে এড়িয়ে বা বিচ্ছিন্ন করে দ্রুত ঢাকায় পৌঁছানো।
৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা-বাগানের ব্যবস্থাপকের বাংলোতে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাথমিক সামরিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এই সভায় কর্নেল এম এ জি ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়াউর রহমানসহ তৎকালীন ২৭ জন ঊর্ধ্বতন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই বাংলাদেশকে চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কর্নেল ওসমানীকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।
১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে মুক্তিযুদ্ধের জন্য মুক্তিবাহিনী ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ ফোর্সেস নামে নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ১১-১৭ জুলাই ১৯৭১ তারিখে কলকাতার ৮ থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ ফোর্সেস সদর দপ্তরে (মুক্তিবাহিনীর প্রধান কার্যালয়) অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারস সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ এবং নিয়মিত বাহিনীর প্রয়োজনে ব্রিগেড (জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স) গঠন করা হয়। এভাবেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটা নিয়মিত বাহিনীর রূপ নেয় এবং এই বাহিনীর মূল ভিত্তি ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা। সব মিলিয়ে এই বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার। এ ছাড়া গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী ছিল প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লাখ বা তারও বেশি। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধার মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১ লাখ ৮০ হাজার থেকে ২ লাখ পর্যন্ত।
আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অপারেশন জ্যাকপট, ব্যাটল অব শিরোমণি, ব্যাটল অব কামালপুর, ব্যাটল অব হিলি, ব্যাটল অব বেলোনিয়া বালজ আমাদের সামরিক ইতিহাসের অংশ এবং গর্বের বিষয়।
ব্যাটল অব বেলোনিয়া বালজ: ১০ নভেম্বর ১৯৭১ সালে ‘ব্যাটল অব বেলোনিয়া বালজ’-এ পাকিস্তানি বাহিনীর একজন মেজরসহ ৭২ জন সৈনিক আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে ১০ ইস্ট বেঙ্গল এবং ভারতীয় বাহিনী শত্রুপক্ষের মূল অবস্থান এড়িয়ে গোপনে তাদের পেছনে অনুপ্রবেশ করে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। এটি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য একটি বড় নৈতিক পরাজয় এবং মুক্তিবাহিনীর জন্য একটি বড় বিজয়। এই যুদ্ধের সফল সামরিক কৌশল বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিসহ বিভিন্ন দেশের সামরিক স্কুলে উদাহরণ হিসেবে পড়ানো হয়।
ব্যাটল অব হিলি: হিলির যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্মুখযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব রণাঙ্গনে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধগুলোর একটি ‘ব্যাটল অব হিলি’ এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের হাতে গোনা কয়েকটি সুসংগঠিত এবং কনভেনশনাল যুদ্ধের অন্যতম। অসংখ্য কংক্রিট বাঙ্কার এবং মাইনফিল্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী এখানে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যার ফলে মিত্রবাহিনী এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। এই যুদ্ধ মূলত দুই পর্বে বিভক্ত ছিল। এর প্রথম পর্ব ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর ১৯৭১ এবং দ্বিতীয় পর্ব ১০ থেকে ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ দুই পর্বে প্রায় ২০ দিন ধরে হিলিতে যুদ্ধ চলে। এই দুই পর্বের যুদ্ধের মাধ্যমে হিলি মুক্ত হয় এবং মিত্রবাহিনী বগুড়ার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হিলির যুদ্ধে মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী উভয়ই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত প্রতিরোধের কারণে উভয় পক্ষেই ব্যাপক হতাহত হয়েছিল।
ব্যাটল অব কামালপুর: ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর কামালপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত সুরক্ষিত ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটির পতন ঘটে। তারা এখানে বাঙ্কার, ট্রেঞ্চ এবং মাইনফিল্ড তৈরি করে এটিকে একটি দুর্গে পরিণত করেছিল। এই ঘাঁটির পতন মানে ছিল ময়মনসিংহ ও ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাওয়া। মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী একত্রে এই ঘাঁটিটি দীর্ঘ ২২ দিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধ ‘ব্যাটল অব কামালপুর’ নামে পরিচিত। মুক্তিযোদ্ধারা এই ঘাঁটি দখলের জন্য বেশ কয়েকবার আক্রমণ চালান। এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১৮টি ছোট-বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষই ব্যাপক হতাহতের শিকার হয়। এই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজের মতো অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের অসম সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ কামালপুরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি বীরত্ব ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে।
অপারেশন ক্যাকটাস লিলি: ১৯৭১ সালের ৯-১২ ডিসেম্বর তারিখে মিত্রবাহিনী মেঘনা নদী পার হওয়ার জন্য একটি সাহসী হেলিকপ্টারভিত্তিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যা ‘অপারেশন ক্যাকটাস লিলি’ বা ‘মেঘনা হেলি ব্রিজ’ নামে পরিচিত। পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর অগ্রাভিযান বাধাগ্রস্ত করার জন্য আশুগঞ্জের ভৈরব সেতু ধ্বংস করেছিল। কিন্তু উক্ত তারিখে ভারতীয় বিমানবাহিনীর এমআই-৪ হেলিকপ্টার ব্যবহার করে প্রায় ১১০টি সর্টির মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আইভি কোর এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মেঘনার পূর্ব পাড় থেকে রায়পুরা (নরসিংদী) এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। এটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সফল ও গুরুত্বপূর্ণ ‘রিভার ক্রসিং’ অপারেশন।
ভার্টিকাল এনভেলপমেন্ট: ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে টাঙ্গাইল এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারাশুট রেজিমেন্টের ২য় প্যারা ব্যাটালিয়নের প্রায় ৭০০ জন প্যারাট্রুপারকে নামানো হয়েছিল। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পরিচালিত সবচেয়ে বড় এয়ারবোর্ন অপারেশনগুলোর মধ্যে একটি। সামরিক ভাষায় এটি ‘ভার্টিকাল এনভেলপমেন্ট’ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যমুনা নদীর ওপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ পুংলি ব্রিজটি দখল করা। এই অপারেশনের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩তম ব্রিগেডকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এই অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কাদের সিদ্দিকীর ‘কাদেরিয়া বাহিনী’র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযান পরিচালনার আগে কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ল্যান্ডিং জোনের স্থান নির্ধারণ করেন। এই অভিযানে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ এবং ল্যান্ডিং জোনের নিরাপত্তার জন্য ওই এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীকে ব্যস্ত রাখা, রোড ব্লক বসিয়ে পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং স্থলপথে সমন্বয় করা।
ব্যাটল অব শিরোমণি: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে খুলনার শিরোমণিতে সংঘটিত ‘ব্যাটল অব শিরোমণি’ একটি বিশেষ কৌশলগত ট্যাংক যুদ্ধ, যা সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বিরল উদাহরণ। শিরোমণির এই যুদ্ধটি ভারত, পোল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ৩৫টি দেশের সামরিক প্রতিরক্ষা কলেজে পড়ানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি এমন একটি বিরল যুদ্ধ, যেখানে একই সঙ্গে ট্যাংক, আর্টিলারি, পদাতিক ও হাতাহাতি যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল।
৩.
যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্রেফ গৃহযুদ্ধ কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা অথবা ইনসারজেন্সি অপারেশন বলে চিহ্নিত করতে চান, তারা আসলে বেইমান এবং অজ্ঞ। একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ কিশোর মুক্তিযোদ্ধা লালু, নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি, মুক্তিযোদ্ধা ইউকে চিং মারমা, ক্র্যাক প্লাটুনের বদি, রুমি, খোকা, আলতাফ মাহমুদ, আবুল বারাক আলভী, লিনু বিল্লাহ, দিনু বিল্লাহ, নুহে আলম বিল্লাহ, খাইরুল আলম, আজম খান, ইমতিয়াজ বুলবুলের রক্ত-ঘামস্নাত স্বাধীনতাযুদ্ধ। স্বাধীনতাযুদ্ধ আমাদের আবেগের জায়গা।

বিএনপির চেয়ারপারসন তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এই শপথ বাক্য পাঠ করান। বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তারেক রহমান।
৮ ঘণ্টা আগে
মন্ত্রিসভায় কীভাবে টেকনোক্র্যাট নেওয়া হয়, কারা এরা, আর ঠিক কী কারণেই ভোটের লড়াইয়ে না নামা এই ব্যক্তিরা হয়ে ওঠেন সরকারপ্রধানের তুরুপের তাস—এমন হাজারো প্রশ্ন এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
১ দিন আগে
সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন জোট বড় ব্যবধানে বিজয় অর্জনের পর সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। নির্বাচনে বিএনপি ও তার মিত্ররা জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।
২ দিন আগে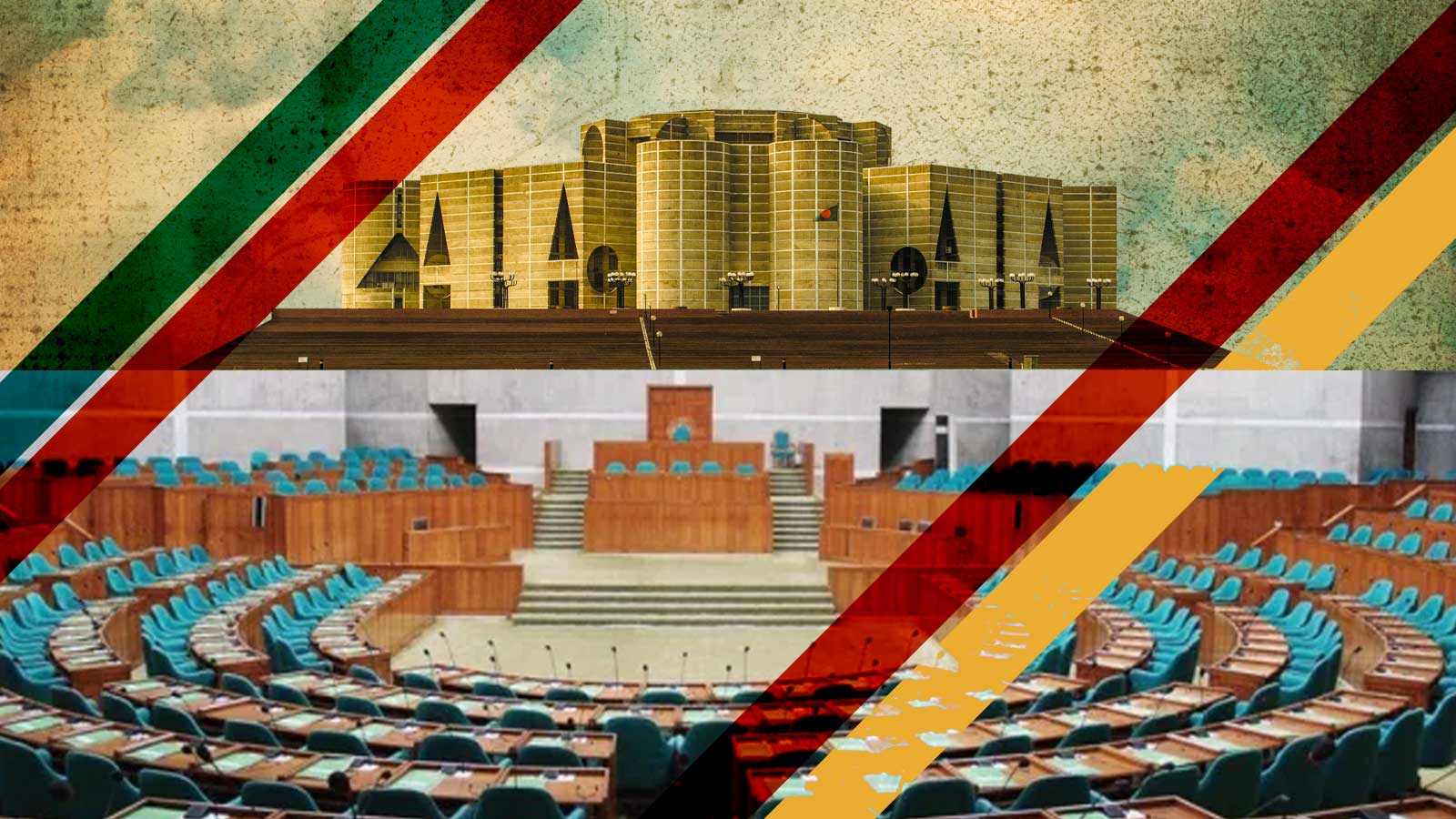
ছায়া মন্ত্রিসভা বিরোধী দলের সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা। এটি ওয়েস্টমিনিস্টার শাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই মন্ত্রিসভার সদস্যদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু তারা ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রীদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।
২ দিন আগে