ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত বার্ষিক ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্সের এবারের আলোচনার শিরোনাম ‘গণতন্ত্র ও উন্নয়ন’, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমরা সবাই এখন এই বিষয়টি নিয়েই ভাবছি। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে আমার মনে হয় তিনটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, একটি কার্যকর জনপ্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ; দ্বিতীয়ত, এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে; এবং তৃতীয়ত, সেই উন্নয়নের গুণগত মান কী হবে। অর্থাৎ, যে উন্নয়ন সংঘটিত হবে, তা একটি ন্যায্য সমাজ গঠন এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে কিনা সেটাই বিবেচ্য। এই তিনটি ভিন্নভিন্ন বিষয় এবং আমি বলব- এগুলো নিয়ে প্রচুর গবেষণার সুযোগ রয়েছে।
তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদের বর্তমান আলাপ-আলোচনা মূলত ওই প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিয়েই আবর্তিত হচ্ছে। এই যে ঐকমত্য কমিশন কিংবা জুলাই সনদ—এগুলো সবই খুব ‘মডেস্ট’ বা সীমিত প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ। এই মুহূর্তে আমাদের প্রত্যাশা- আমরা যেন অন্তত একটি কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি। স্বাধীনতার প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক পরেও আমাদের এই লক্ষ্যটি আমার কাছে সীমিতই মনে হচ্ছে। কারণ, এটি মূলত দেশ শাসনের একটি কার্যকর বন্দোবস্ত তৈরি করা মাত্র। এতদিন পরেও আমাদের লক্ষ্য এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকাটা দুঃখজনক। তবুও আমরা আশা করব, নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, সেখানে হয়তো আমরা আরও দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই বন্দোবস্তের দিকে এগোতে পারব।
গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন নিয়ে প্রচুর গবেষণা ও লেখালেখি হয়; এটি অত্যন্ত বিস্তৃত একটি বিষয়। ফলে এটা নিয়ে কথা বলতে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয় যে- এই বিস্তৃত বিষয়ের কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। এছাড়া এত সব বিষয় নিয়ে সুস্থির মনে তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা করার মতো মানসিক অবস্থাও আমার নেই। সে কারণে আমি আমার লেখা ইদানীং কালের দুটো বইয়ের আলোকে কথা বলতে চাই। একটি বইয়ের নাম ‘উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ এবং অন্যটি ‘মার্কেটস, মরালস এন্ড ডেভেলপমেন্ট: রি-থিংকিং ইকোনমিকস ফ্রম এ ডেভেলপিং কান্ট্রি পারসপেক্টিভ’। সারা বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মূল সমস্যাটি হলো—একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে অর্থনীতি হবে প্রধানত মুনাফা-তাড়িত, ব্যক্তিনির্ভর এবং বাজারভিত্তিক; আবার তাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণও থাকবে। এমন একটি গণতান্ত্রিক বাজারভিত্তিক ব্যবস্থায় আমরা একইসঙ্গে একটি ন্যায্য সমাজ চাই এবং বৈষম্যও কমিয়ে রাখতে চাই। এটি কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের কোনো একক সমাধান নেই। আমি নিজে যা চিন্তা করেছি, তা উপরে উল্লিখিত বই দুটিতে মোটামুটি লিখেছি। তবে এখন আরও নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।
আসলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং পরিবেশের ওপর। এর কোনো একক সমাধান অন্য দেশ থেকে ধার করে আনা সম্ভব নয়। যেমন—আমরা যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই যা সুষম এবং দারিদ্র্য নিরসনকারী হবে, তবে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো হতে হবে—বিষয়টি এমন নয়। ভালো ক্রিকেট খেলতে চাইলেই যেমন শচীন টেন্ডুলকারের মতো খেলা যায় না, ব্যাপারটা তেমনই। প্রতিটি দেশকেই তার নিজস্ব পথ খুঁজে বের করতে হয়।
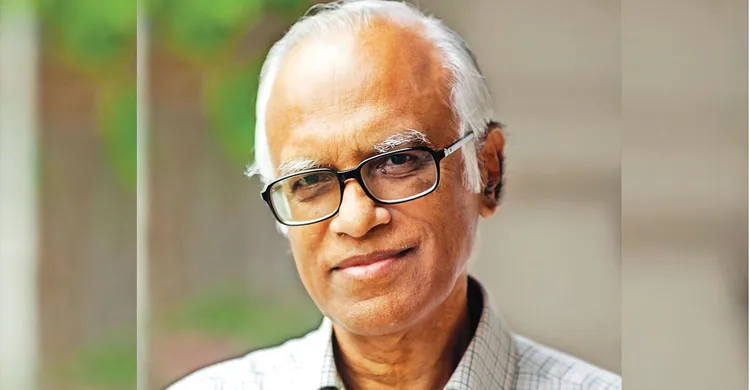
আমি আগেই বলেছি যে, খুব সুস্থিরভাবে নতুন কোনো অ্যাকাডেমিক ভাবনা-চিন্তার অবকাশ আমি পাচ্ছি না। কারণ হলো, আমি একটি দৈবক্রমে গঠিত সরকারের দৈবক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা। সেখানে গবেষণা বা লেখালেখির সুযোগ নেই। তবে একটা সুবিধা আছে—তা হলো, এতদিন যেসব গবেষণা বা লেখালেখি করেছি, সেগুলোর ধারণার সঙ্গে বাস্তবের কতটুকু মিল আছে তা যাচাই করা। আমরা অনেকেই গবেষণায় বলি—কেন এটা করা হচ্ছে না, কেন ওটা আরও ভালো হচ্ছে না, কেন এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে এগুলোর অনেক সময় মিল থাকে না, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে।
আমি আগেই বলেছি, এই মুহূর্তে আমরা যেসব সংস্কারের কথা বলছি, তার লক্ষ্য হলো কার্যকর গণতন্ত্রের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। যেখানে একটি নির্বাচিত সংসদ থাকবে এবং সেই সংসদের মাধ্যমে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। সেই সঙ্গে কিছু অনির্বাচিত কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকবে—যা যেকোনো দেশেই থাকে—যেমন: স্বাধীন বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম এবং নাগরিক সক্রিয়তা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ভালো গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাস্তবে এসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঠিকঠাক থাকলেও গণতন্ত্রের গুণগত মান শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে রাজনৈতিক আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতির ওপর। এটাই আসল কথা এবং এই সংস্কৃতি একদিনে গড়ে ওঠে না, ধীরে ধীরে তৈরি হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে ‘টুয়েন্টি ইয়ার্স অফ রিফর্মস’ নামে একটি বিখ্যাত বই আছে। বইটি মূলত দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কার নিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অনেকটা বাংলাদেশের মতোই ছিল—সার্কিট জাজ থেকে শুরু করে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সব জায়গাই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। নিয়ম-নীতির বালাই ছিল না, ছিল মাফিয়া তন্ত্র। মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সেই সংস্কৃতি বদলে আমেরিকা কীভাবে একটি নিয়মবদ্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আসতে পারল, তা লক্ষণীয়। আমরা অতীতে যা দেখেছি, তা বদলাতে হবে। রাজনীতি যদি জনকল্যাণমুখী না হয়ে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা বিতরণের হাতিয়ার হয়—যা আমরা এতদিন দেখে এসেছি—তাহলে যুবসমাজের একটি বড় অংশ ‘ক্যাডার ভিত্তিক’ রাজনীতি বা চাঁদাবাজিকেই জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। শুধু তাই নয়, একটি সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কেবল ব্যবসার পরিবেশই নষ্ট করে না (যাকে আমরা ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’ বলি), বরং তারা অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণকেও নিজেদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসে। এর ফলে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
আমার মনে হয়, একটি বিষয় হয়তো কেউ সেভাবে তুলে ধরেননি—তা হলো আমাদের শিক্ষার নিম্নমান এবং বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়া। এর সঙ্গে যুব বেকারত্ব ও যুবসমাজের একাংশের রাজনৈতিক ক্যাডারভিত্তিক জীবিকার প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি পরস্পর সম্পর্কিত। এই সমস্যাগুলোর সমাধান পৃথকভাবে করা সম্ভব নয়। আমরা হয়তো এভাবে বিষয়টি ভেবে দেখিনি। তাই শুধু রাজনীতির ওপর দোষ চাপালেই চলবে না; আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বেকার সমস্যার দিকেও নজর দিতে হবে।
ধরলাম, আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—সেই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে নিশ্চিত হবে? শুধু গণতন্ত্র থাকলেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাছাড়া বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশই বা কীভাবে তৈরি হবে? এটি তো শুধু সরকারের একার বিষয় নয়। বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক সূচক রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ সবসময়ই পিছিয়ে। একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়—যদিও আমরা অনেকে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না—যে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা কমালে বা লাইসেন্স পাওয়ার সময় কমিয়ে আনলেই ব্যবসার পরিবেশ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কেবল আমলাতান্ত্রিক সমাধান দিয়ে এই পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।
আমাদের দেশে ব্যবসায়ী এবং আমলা বা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যদি একটি অশুভ লেনদেন বা আঁতাতের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তবে তা কেবল প্রশাসনিক সংস্কার দিয়ে হঠাৎ করে ঠিক করা যায় না। এটি সত্য যে, আমরা নতুন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান তৈরি করতে পারি, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং এতে কিছু সমস্যার সমাধানও হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই—এই বছর থেকে—অনলাইনে আয়কর জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছি। এর ফলে কর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ আর নেই, যা নিঃসন্দেহে সাধারণ করদাতাদের হয়রানি বন্ধ করবে। এটি অবশ্যই কার্যকর একটি পদক্ষেপ। কিন্তু বড় বড় কর ফাঁকির ঘটনাগুলো যে শুধু অনলাইনে কর ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাধান হবে, তা নিশ্চিত নয় বা আমি তা মনেও করি না। সেটির জন্য আরও বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। মোদ্দাকথা হলো, আমরা আইন-কানুন বা বিধি-বিধান দিয়ে যা-ই করতে চাই না কেন, সেটার ফলাফল নির্ভর করবে ওই দেশের তৎকালীন ব্যবসায়িক-আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা আচরণবিধির ওপর—যাকে আমরা বলি ‘সোশ্যাল সুপার স্ট্রাকচার’। আমরা যেসব নতুন বিধি-বিধান দিচ্ছি, সেগুলো কী ধরনের প্রণোদনা বা ইনসেনটিভ তৈরি করছে, তা এই কাঠামোর ওপরই নির্ভর করে। আমি যদি ওই পরিবেশ বা আচরণকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে ভুলভাবে নতুন বিধি-বিধান চাপিয়ে দিই, তবে তার ফলাফল অনির্দিষ্ট হতে পারে। যদি সেটি কার্যকর হয়, তবে হয়তো উৎপাদনশীল উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। কিন্তু কার্যকর না হলে তা উল্টো ‘রেন্ট সিকিং’ বা অবৈধ উপার্জনের দিকেই মানুষকে ঠেলে দেবে। তখন মনে হবে আমরা ভালো বিধি-বিধান করছি, কিন্তু আদতে তা অবৈধ উপার্জনের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।
আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কারের অধীনে বলা হতো—ঢালাওভাবে উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ করে যাও, তাহলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং সব সমস্যার সমাধান মিলবে। কিন্তু ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক নিজেই একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানায় যে, তাদের এই উদারীকরণ ও সংস্কারের পরামর্শ একেক দেশে একেক রকম ফলাফল দিয়েছে। কোনো দেশে ভালো ফল মিলেছে, আবার কোনো দেশে উল্টো ক্ষতি হয়েছে। এর কারণ হলো, একটি দেশের আচরণবিধি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ ‘রিলেশনশিপ অফ ট্রাস্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন’ কেমন—তার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে। একে ‘সোশ্যাল ক্যাপিটাল’ বা সামাজিক মূলধনও বলা হয়। আমরা যখন নতুন বিধি-বিধান চাপিয়ে দিই, তখন সেটির কার্যকারিতা কতটুকু হবে, তা মূলত এই সামাজিক মূলধনের ওপরই নির্ভর করে।
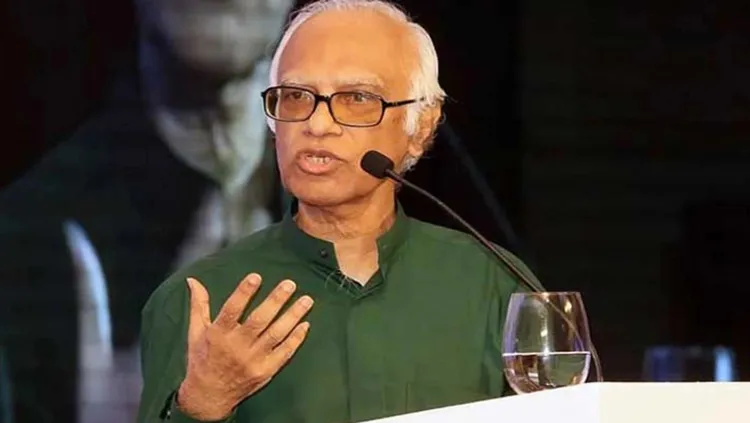
আমি দু-একটি উদাহরণ দিতে চাই। আগেই বলেছি, নতুন করে ভাবার সময় আমি পাইনি, তবে কিছু উদাহরণ আমি লক্ষ্য করেছি। যেমন—ভারতে ঘুষ নেওয়া যেমন ফৌজদারি অপরাধ (ক্রিমিনাল অফেন্স), তেমনি ঘুষ দেওয়াও অপরাধ। আমাদের অনেকের পরিচিত কৌশিক বসু, যিনি একসময় ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ঘুষ দেওয়াও যদি অপরাধ হয়, তবে কেউ আর ‘হুইসেল ব্লোয়ার’ হবে না। অর্থাৎ, কেউ নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলবে না যে—অমুক কর্মচারী আমার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ঘুষ দেওয়াকে যেন অপরাধ হিসেবে গণ্য না করা হয়। কিন্তু তখন ভারতের গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজে এ নিয়ে তুমুল হইচই পড়ে যায়। তারা মনে করেছিলেন, এটি একটি অনৈতিক প্রস্তাব যা ঘুষ দেওয়াকে বৈধতা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।
বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলাম, বাংলাদেশে ঘুষ নেওয়া অপরাধ হলেও ঘুষ দেওয়াকে সবসময় সেভাবে অপরাধ হিসেবে দেখা হয় না। কিন্তু তারপরও তো খুব একটা লাভ হয়নি। এর কারণ হলো, যখন কোনো অবৈধ সুবিধা আদায়ের জন্য—যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য—ঘুষ দেওয়া হয়, তখন যিনি দিচ্ছেন তিনিও বিষয়টি প্রকাশ করবেন না। বাংলাদেশ বা আমাদের মতো দেশগুলোতে অনেক ঘুষ লেনদেন হয় ‘স্পিড মানি’ হিসেবে। এতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ থাকে, তাই কেউই এ নিয়ে কথা বলে না।
আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘সরকারি ক্রয় নীতি সংশোধন ২০২৫’ পাস হয়েছে এবং এটি এখনই কার্যকর। সরকারি ব্যয়ের বিশাল অংশ—উন্নয়ন বাজেট, পরিচালন বাজেট, রাজস্ব বাজেট—সবকিছুই এই ক্রয় নীতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা একদম উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য হলো ঠিকাদারি খাতের একচেটিয়া প্রভাব ভাঙা। আমরা দেখেছি, রেলওয়ে বা সড়ক ও জনপথের মতো বিভিন্ন খাতে দু-তিনটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বা একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে কাজগুলো কুক্ষিগত করে রেখেছে। নতুন নীতিমালার অধীনে টেন্ডার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ওই সেক্টরের অতীত অভিজ্ঞতাই এখন আর মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়। বেনামে ঠিকাদারি নেওয়ার কোনো সুযোগ আর থাকছে না; অর্থাৎ প্রভাব খাটিয়ে কাজ নিয়ে অন্যকে দিয়ে করানো যাবে না। এতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। যারা হয়তো আগে কখনো টেন্ডারে অংশ নেয়নি কিন্তু ভালো ব্যবসায়ী, যাদের কর ও ব্যবসার নথিপত্র স্বচ্ছ—তাদের এখন পার্টনার হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।
যাইহোক, এগুলো আমার মূল কথা নয়। আমি আসলে যেটা বলতে চেয়েছি তা হলো, টেন্ডারের মূল্যায়ন পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। কোনো একটি দেশে টেন্ডার মূল্যায়নের আদর্শ পদ্ধতি কী হবে, তার কোনো ধরাবাঁধা ফর্মুলা নেই। এটি মূলত নির্ভর করে যে সরকারি কর্তৃপক্ষ টেন্ডার আহ্বান করছে এবং যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আবেদন করছে—এই দুই পক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। বিভিন্ন দেশে এই পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। যদি উভয় পক্ষকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হয়—আমাদের ক্ষেত্রে যা দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে, যেখানে টেন্ডার আহ্বানকারী কর্মকর্তাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন এবং ঠিকাদার যে কুকর্ম করবেন না তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই—সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতিকে একদম নিয়মবদ্ধ করে দিতে হয়। সেখানে কোনো ‘ডিসক্রিপশন’ বা নমনীয় মূল্যায়নের সুযোগ রাখা যায় না।
তবে এর একটি নেতিবাচক দিকও আছে। যদি আমি কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হতাম, তবে আমি নমনীয়ভাবে চাইতাম যেন সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই কাজটা পায়; কেবল নিয়ম-নীতির ফর্মুলার মধ্যে আটকে না থেকে নিজের বিবেচনা ব্যবহার করতাম। কিন্তু এখানেই একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়—একদিকে কীভাবে দুর্নীতির সুযোগ কমানো যাবে, আর অন্যদিকে কীভাবে প্রকৃত ভালো দরদাতা বাছাই করা যাবে। আমি এ কথাটি বললাম কারণ, এই ফর্মুলাটি কী হবে তা নির্ভর করে ওই দেশে এই দুই পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার সংস্কৃতি কতটা গড়ে উঠেছে তার ওপর। হয়তো ভবিষ্যতে এই ফর্মুলা বদলানো যাবে বা আরও নমনীয় করা যাবে, যখন আমরা দেখব যে সত্যিই ভালো ভালো ঠিকাদার এসেছে, তাদের বিশ্বাস করা যায় এবং কর্তৃপক্ষও আরও সৎ হয়েছে।
আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সেটি হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উৎপাদিত পরিসংখ্যান, বিশেষ করে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হিসাব। এসব পরিসংখ্যান বিবিএস নিজেরা সরাসরি প্রকাশ করে না; সরকারের মন্ত্রীকে তা অনুমোদন করতে হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সন্দেহ তৈরি হয়েছে। একটি হলো বিবিএস-এর সক্ষমতার বিষয়। যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে তারা যেসব পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে, সেগুলোর মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকে এবং গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থাকে। আরেকটি হলো, সরকার প্রভাব বিস্তার করে মূল্যস্ফীতি কম দেখাতে চাচ্ছে কি না, কিংবা জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেখাতে চাচ্ছে কি না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এমনটা প্রায়ই ঘটে। আসলে জিডিপি বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি খুব ভালো একটি সূচক নয়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ভালো হলেই যে সবার কল্যাণ সাধিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। ১৯৩০-এর দশকে বা ৪০-এর দশকের শুরুতে যখন সাইমন কুজনেট জিডিপি ধারণাটি তৈরি করেন, তখন তা মূলত যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ তৈরির জন্য করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ৫০-এর দশকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্সের রিচার্ড স্টোন এবং কেইনসের ছাত্ররা মিলে ‘ইনপুট-আউটপুট টেবিল’ ব্যবহার করে জিডিপিকে আজকের কাঠামোতে রূপ দেন।
যাই হোক, আমি বলছিলাম যে বিবিএস-এর সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং আমরা তা নিয়ে ভাবছি। হোসেন জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠেছে—বিবিএসকে স্বাধীন করে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? স্বাধীন করলেও তো যেকোনো প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত সরকারের অধীনেই থাকে এবং সক্ষমতার বিষয়টিও থেকে যায়। তার চেয়েও বড় কথা—আমার নিজের বিশ্বাস, এবং এ কারণেই কিছু বিধি-বিধান ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং পরিসংখ্যান আইনে নতুন ধারা সংযুক্ত করার উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি—তা হলো বিবিএস-এর স্বাধীনতার চেয়েও বেশি জরুরি হলো তাদের উৎপাদিত পরিসংখ্যান ও তথ্যের স্বচ্ছতা।
জিডিপির প্রবৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করতে অসংখ্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই ব্যক্তিগত তথ্য নয়; এগুলো অন্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তিগত কোনো পরিসংখ্যান হলে আন্তর্জাতিক প্রোটোকল অনুযায়ী ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হয়। যেমন—সার্ভে বা জরিপ প্রকাশ করার সময় ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে যেন চেনা না যায়, তা নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু জিডিপি বা মূল্যস্ফীতির হিসাব তো আসে অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, যেখানে গোপনীয়তার কোনো অবকাশ নেই। কাজেই জিডিপি কীভাবে মাপা হচ্ছে, প্রবৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতি কীভাবে প্রতি বছর হিসাব করা হচ্ছে, কোন বাজারের কোন জায়গা থেকে কোন সামগ্রীর দাম প্রতি সপ্তাহে নেওয়া হচ্ছে—এসবের মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই। আমার সামনে সাংবাদিক রিজভী বসে আছেন; আমি তাঁকেই বলছি—আপনি যদি সন্দেহ করেন যে মূল্যস্ফীতি কম দেখানো হচ্ছে অথচ বাজারে দাম বেশি, তবে বিবিএস-এ যান। আমি এখনই বিষয়টিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আপনারা যাচাই করুন—আলু বা পেঁয়াজের দাম ঠিক কোন কোন বাজার থেকে নেওয়া হয়েছে। যদি মনে হয় সেটা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না, তাহলে প্রশ্ন তুলুন যে এটা ঠিক হয়নি। এই স্বচ্ছতাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।
এই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়তো এখন একটু কঠিন, তবে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানকেই ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। বিবিএসকেও সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। একবার ডিজিটালাইজড হয়ে গেলে এই তথ্যের প্যাকেজগুলো যেকোনো গবেষক বা সাংবাদিক চাইলেই নিতে পারবেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন। এতে সুবিধা হবে এই যে, গবেষকরা পরামর্শ দিতে পারবেন—'এই পরিমাপের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো একটি পরিসংখ্যানের উৎস ছিল, সেটি ব্যবহার করলে ফল আরও নির্ভুল হতো।' ফলে বিবিএস-এর তথ্য ভাণ্ডারও আরও সমৃদ্ধ হবে।

সংস্কারের এই বিষয়গুলো বললাম, যাকে প্রাতিষ্ঠানিক বা আমলাতান্ত্রিক সংস্কার বলা যায়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, অবৈধ আয় বা ‘রেন্ট সিকিং’ কমাতে গেলে তা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, যদি অবৈধ আয়ের উপার্জনের একটি রাজনৈতিক চাহিদা থাকে, তবে শুধু নতুন আইন বা বিধি-বিধান দিয়ে তা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা যায় না। আমি যদি আয়ের একটি অবৈধ উৎস বন্ধ করে দিই, তবে অন্য আরেকটি উৎস খুঁজে বের করা হবে। অতীতে আমরা ঠিক এমনটাই ঘটতে দেখেছি।
যেকোনো রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থাতেই উন্নয়নের অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সফল ও ব্যর্থ—উভয় ধরনের উন্নয়নের দৃষ্টান্তই রয়েছে। সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হোক, একনায়কতান্ত্রিক হোক, স্বৈরশাসন হোক, কিংবা মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দীর্ঘদিনের একদলীয় প্রাধান্যের শাসন হোক—সব ধরনের শাসনব্যবস্থাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভালো হতে পারে। শুধু গণতন্ত্রই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক, বিষয়টি তা নয়। বরং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি—দুই-তিন দশক ধরে ক্রমাগতভাবে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপরে থাকা। যেমনটা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং ইস্ট এশিয়ান মিরাকল ইকোনমিগুলোতে হয়েছিল। বর্তমানে চীনে যা হচ্ছে, ভিয়েতনামে কিছুটা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ায় নতুন করে যুক্ত হচ্ছে এবং মালয়েশিয়ায় অনেক আগেই সেই উত্তরণ ঘটেছে।
এই সবগুলো দেশের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমি আমার বইতে প্রথম উল্লেখ করেছিলাম। সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হলো ‘অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজম ইন দ্য গভর্নেন্স সিস্টেম’ বা শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার কাঠামো। প্রশাসন যন্ত্রের সকল পর্যায়ে একটি শক্ত জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার বিষয়টি তো আমরা জানিই—সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত সংসদ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কিন্তু আমরা অনেক সময় যা লক্ষ্য করি না তা হলো—চীনে ১৯৮০-র দশকে যখন বাজারমুখী সংস্কার শুরু হলো, তখন সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির একদলীয় শাসন থাকা সত্ত্বেও দলের ভেতরেই একটি বড় ধরনের সংস্কার করা হয়েছিল। সেটি হলো—প্রত্যেকটি স্তরে যারা অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের সময়ভিত্তিক ও ফলাফলভিত্তিক প্রতিটি নীতির সফলতা নিয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। নিয়মটা ছিল এমন—তুমি নীতি নির্ধারণ করো, সফল হও, তাহলে ভালো ফল পাবে; আর বিফল হলে চাকরিচ্যুত হবে। ভিয়েতনামেও ১৯৯০-এর দশকে যখন বাজার অর্থনীতি নীতি চালু হলো, তখন তারাও তাদের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে এই ধরনের সংস্কার এনেছিল।
এই প্রসঙ্গে আমি এটাও বলব যে, একটি দেশের আচরণবিধি, মূল্যবোধ এবং একে অপরের প্রতি আস্থা ও সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে উদারীকরণ কতদূর সফল হবে। ভিয়েতনামের বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই আশ্চর্যজনক। যখন তারা প্রথম বাজার অর্থনীতির উদারীকরণ করে, তখন তারা ভাবেনি যে এর জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো লাগবে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা একচেটিয়া ব্যবসা থামানোর জন্য আইন করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভিয়েতনামের ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নিজেরাই একত্রে বসে ঠিক করলেন যে, তারা কীভাবে নিয়মের ভেতর চলবেন। তারা স্থির করলেন যে, কেউ একে অপরের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় যাবেন না, মূল্যহার প্রতিযোগিতামূলক রাখবেন এবং ঋণ নিলে তা ফেরত দেবেন। এটি সম্পূর্ণই একটি সাংস্কৃতিক বিষয়।
আমি যখন এই জবাবদিহিতা বা ‘অ্যাকাউন্টেবিলিটি’ নিয়ে কথা বলেছিলাম—অনেকের হয়তো মনে আছে, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরেও আমি বলেছিলাম যে, সফল দেশে সকল স্তরের প্রশাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতাই মূল বিষয়। তখন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন একটি বিষয় যোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জবাবদিহিতাই সব নয়, এর সঙ্গে দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। জবাবদিহিতা বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি হলো একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আর দায়িত্ববোধ বা ‘সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি’ হলো একটি নৈতিক আচরণের বিষয়।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগের কালের একজন মফস্বলের এলএমএফ পাস করা ডাক্তার—তিনি ঠিক সময়ে অফিসে আসছেন কি না বা রোগী দেখছেন কি না, সেটা হলো তাঁর জবাবদিহিতা। কিন্তু তিনি যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের খোঁজ নেন, কোনো গরিব রোগী খুব অসুস্থ হলে তাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন—সেটা তো জবাবদিহিতা নয়, সেটা হলো দায়িত্ববোধ। প্রাইমারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই। এখনকার অনেক প্রাইমারি শিক্ষক ছাত্রদের জিম্মি করে পরীক্ষা বন্ধ রেখে স্ট্রাইকে যাচ্ছেন। অথচ আমার ছোটবেলায় প্রাথমিক শিক্ষকরা আমার বাসায় এসে খোঁজ নিতেন যে, আমার অঙ্কে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না বা ইংরেজিতে কোনো অসুবিধা আছে কি না। এটাই হলো দায়িত্ববোধ।
আমি তৃতীয় যে বিষয়টি বলেছিলাম—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতিতে কীভাবে একটি ন্যায্য সমাজ এবং বৈষম্য নিরোধক উন্নয়ন সম্ভব হবে? বর্তমানে আমরা জুলাই সনদ বা ঐক্যমত কমিশন নিয়ে যেসব আলোচনা করছি, সেখানে এই বিষয়গুলো নেই। এটা স্বাভাবিক, কারণ এই বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয়। এখানে নীতি নির্ধারণের অনেক বিষয় আছে। এখানেই বাম, ডান, মধ্য-ডান বা মধ্য-বাম—এ ধরনের আদর্শগত দলের পার্থক্য তৈরি হয়। তাই নীতির ব্যাপারে এখানে ঐকমত্য হবে না, এবং সে কারণেই এটি এখন আলোচিত হচ্ছে না। তবে আমরা আশা করব, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এবার আসা যাক ‘ন্যায্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা’ ঠিক কি সেই আলোচনায়। আসলে এখানে ন্যয্যতার সংজ্ঞাটি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। শুধু ‘ন্যায্য অর্থনীতি’ বা ‘বৈষম্যহীন অর্থনীতি’ বললেই বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। কী ধরনের বৈষম্যহীনতা? এর সংজ্ঞা নিয়ে দার্শনিকরাও দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করেও কোনো একক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।
সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচিগুলোর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কীভাবে হবে? শুধু সুরক্ষা দেব বা দারিদ্র্য কমে যাবে বললেই তো হবে না। এই সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারের যে আয়ের প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে বা কী কর-নীতির মাধ্যমে আসবে? আয় পুনর্বণ্টন করতে হলে কর ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? বাজার ও রাষ্ট্রের সম্পর্কই বা কী রকম হবে, যাতে একচেটিয়া ব্যবসা তৈরি না হয় এবং মুনাফা-তাড়িত ব্যবসাকে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা যায়? উদ্যোক্তাদের জন্য সমান সুযোগ কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে? কয়েকজন বড় বড় শিল্পপতি যেন পুরো নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়াকে কুক্ষিগত করতে না পারেন, তার ব্যবস্থা কী হবে? সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কীভাবে ক্ষমতায়িত করা যাবে?

এছাড়া পরিবেশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে—আমাদের মতো দেশে এটিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আমরা যখন কোনো ‘কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস’ (ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ) করি, তখন একটি ‘ডিসকাউন্ট রেট’ ধরি এবং সাধারণত ৩০ বছরের মেয়াদে সেই হিসাব করি। আজকের ১০ টাকার ক্ষতি এবং ৩০ বছর পরের ১০ টাকার ক্ষতিকে আমরা এক করে দেখি না; ভবিষ্যতের ক্ষতিকে আমরা অনেক কম গুরুত্ব দিই। আমার জীবদ্দশায় বা একটি প্রজন্মের জীবদ্দশায় আমি ভবিষ্যৎকে কম গুরুত্ব দিতেই পারি। কিন্তু আমরা যখন পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করছি, তখন আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবছি। পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থকে ‘ডিসকাউন্ট’ করার বা খাটো করে দেখার নৈতিক অধিকার আমাকে কে দিল? আমার কাছে যদি পরিবেশের ক্ষতি ১০ টাকা হয়, তবে আমার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কেন তা ১০ টাকার চেয়ে কম হবে? এটি অর্থনীতিবিদদের কাছেও একটি বিরাট প্রশ্ন, যার সমাধান এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও এ বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন গবেষক উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা পরিবেশবাদীরা গ্রহণ করেননি।
আমার বই দুটোতে মূলত এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো, এগুলো নিয়ে বিশদ কথা বলার সময়ও এখন নেই। তাছাড়া এই বইগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আমার দল-নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হতে পারে এবং আমার আদর্শগত অবস্থান প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। বর্তমান সময়ে ‘ট্যাগিং’ বা তকমা দেওয়ার যে প্রবণতা চলছে, তাতে বিষয়টি বেশ বিপদজনক।
তবে আমি দুটি সাধারণ বা মৌলিক প্রতিপাদ্য দিয়ে শেষ করতে চাই, যা আমার সহকর্মী গবেষকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আশা করি: এক. কোনো দেশই এত দরিদ্র নয় যে তার সকল নাগরিকের ন্যূনতম জীবিকা ধারণের চাহিদা মেটাতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন কেবল উপযুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। দুই. লর্ড মেইনার্ড কেইনস সুশাসনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাংক অনেক পরে এসে আমাদের সুশাসন শেখাতে গেছে, কিন্তু তার বহু আগে ১৯৩০-এর দশকে কেইনস বলেছিলেন—সুশাসন হলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় বা ভারসাম্য রক্ষা করা। এর থেকে একটি অনুসিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে। যদিও অর্থনীতিবিদরা আয় বণ্টনের অনেক বিকল্প তত্ত্ব দিয়ে থাকেন—যাকে নিও-ক্লাসিক্যাল, কেইনসিয়ান বা ক্যালেস্কিয়ান তত্ত্ব বলা হয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয় বণ্টন কীভাবে নির্ধারিত হবে, তা হয়তো নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর। এটি আমার কথা নয়; ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি বলেছেন। যিনি ‘ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি’ লিখেছেন। পিকেটি বলেছিলেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো বৈষম্য বাড়িয়ে দেওয়া। ২০১৫ সালের দিকে প্রকাশিত তাঁর ‘দ্য ইকোনমিকস অফ ইনইকুয়ালিটি’ বইয়ে তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আয় বণ্টনের যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উত্থানের সম্পর্ক অত্যন্ত জোরালো।
পরিশেষে, আজকের এই আয়োজনের জন্য বিআইডিএসকে ধন্যবাদ জানাই। যারা এখানে যোগ দিয়েছেন—সংবাদকর্মী, অংশগ্রহণকারী এবং যারা প্রবন্ধ পাঠ করবেন—সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি।
লেখক: অর্থনীতিবিদ ও অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা
৭ ডিসেম্বর বিআইডিএসের বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের ভিত্তিতে প্রণীত। অনুলিখন: মুজাহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত বার্ষিক ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্সের এবারের আলোচনার শিরোনাম ‘গণতন্ত্র ও উন্নয়ন’, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমরা সবাই এখন এই বিষয়টি নিয়েই ভাবছি। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে আমার মনে হয় তিনটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, একটি কার্যকর জনপ্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ; দ্বিতীয়ত, এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে; এবং তৃতীয়ত, সেই উন্নয়নের গুণগত মান কী হবে। অর্থাৎ, যে উন্নয়ন সংঘটিত হবে, তা একটি ন্যায্য সমাজ গঠন এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে কিনা সেটাই বিবেচ্য। এই তিনটি ভিন্নভিন্ন বিষয় এবং আমি বলব- এগুলো নিয়ে প্রচুর গবেষণার সুযোগ রয়েছে।
তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদের বর্তমান আলাপ-আলোচনা মূলত ওই প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিয়েই আবর্তিত হচ্ছে। এই যে ঐকমত্য কমিশন কিংবা জুলাই সনদ—এগুলো সবই খুব ‘মডেস্ট’ বা সীমিত প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ। এই মুহূর্তে আমাদের প্রত্যাশা- আমরা যেন অন্তত একটি কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি। স্বাধীনতার প্রায় সাড়ে পাঁচ দশক পরেও আমাদের এই লক্ষ্যটি আমার কাছে সীমিতই মনে হচ্ছে। কারণ, এটি মূলত দেশ শাসনের একটি কার্যকর বন্দোবস্ত তৈরি করা মাত্র। এতদিন পরেও আমাদের লক্ষ্য এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকাটা দুঃখজনক। তবুও আমরা আশা করব, নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, সেখানে হয়তো আমরা আরও দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই বন্দোবস্তের দিকে এগোতে পারব।
গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন নিয়ে প্রচুর গবেষণা ও লেখালেখি হয়; এটি অত্যন্ত বিস্তৃত একটি বিষয়। ফলে এটা নিয়ে কথা বলতে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয় যে- এই বিস্তৃত বিষয়ের কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। এছাড়া এত সব বিষয় নিয়ে সুস্থির মনে তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা করার মতো মানসিক অবস্থাও আমার নেই। সে কারণে আমি আমার লেখা ইদানীং কালের দুটো বইয়ের আলোকে কথা বলতে চাই। একটি বইয়ের নাম ‘উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র’ এবং অন্যটি ‘মার্কেটস, মরালস এন্ড ডেভেলপমেন্ট: রি-থিংকিং ইকোনমিকস ফ্রম এ ডেভেলপিং কান্ট্রি পারসপেক্টিভ’। সারা বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মূল সমস্যাটি হলো—একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে অর্থনীতি হবে প্রধানত মুনাফা-তাড়িত, ব্যক্তিনির্ভর এবং বাজারভিত্তিক; আবার তাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণও থাকবে। এমন একটি গণতান্ত্রিক বাজারভিত্তিক ব্যবস্থায় আমরা একইসঙ্গে একটি ন্যায্য সমাজ চাই এবং বৈষম্যও কমিয়ে রাখতে চাই। এটি কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের কোনো একক সমাধান নেই। আমি নিজে যা চিন্তা করেছি, তা উপরে উল্লিখিত বই দুটিতে মোটামুটি লিখেছি। তবে এখন আরও নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।
আসলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং পরিবেশের ওপর। এর কোনো একক সমাধান অন্য দেশ থেকে ধার করে আনা সম্ভব নয়। যেমন—আমরা যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই যা সুষম এবং দারিদ্র্য নিরসনকারী হবে, তবে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো হতে হবে—বিষয়টি এমন নয়। ভালো ক্রিকেট খেলতে চাইলেই যেমন শচীন টেন্ডুলকারের মতো খেলা যায় না, ব্যাপারটা তেমনই। প্রতিটি দেশকেই তার নিজস্ব পথ খুঁজে বের করতে হয়।
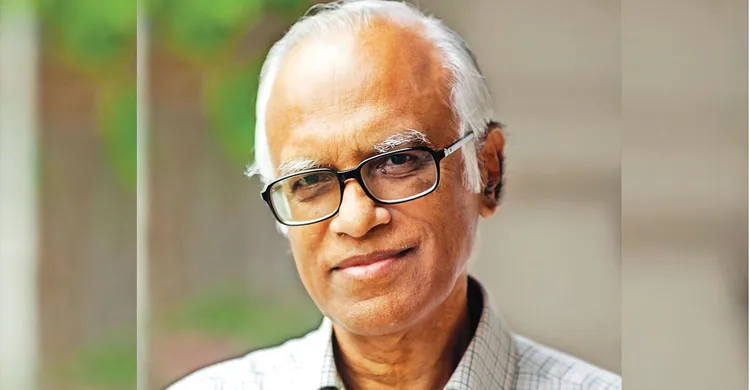
আমি আগেই বলেছি যে, খুব সুস্থিরভাবে নতুন কোনো অ্যাকাডেমিক ভাবনা-চিন্তার অবকাশ আমি পাচ্ছি না। কারণ হলো, আমি একটি দৈবক্রমে গঠিত সরকারের দৈবক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা। সেখানে গবেষণা বা লেখালেখির সুযোগ নেই। তবে একটা সুবিধা আছে—তা হলো, এতদিন যেসব গবেষণা বা লেখালেখি করেছি, সেগুলোর ধারণার সঙ্গে বাস্তবের কতটুকু মিল আছে তা যাচাই করা। আমরা অনেকেই গবেষণায় বলি—কেন এটা করা হচ্ছে না, কেন ওটা আরও ভালো হচ্ছে না, কেন এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে এগুলোর অনেক সময় মিল থাকে না, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে।
আমি আগেই বলেছি, এই মুহূর্তে আমরা যেসব সংস্কারের কথা বলছি, তার লক্ষ্য হলো কার্যকর গণতন্ত্রের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। যেখানে একটি নির্বাচিত সংসদ থাকবে এবং সেই সংসদের মাধ্যমে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। সেই সঙ্গে কিছু অনির্বাচিত কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকবে—যা যেকোনো দেশেই থাকে—যেমন: স্বাধীন বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম এবং নাগরিক সক্রিয়তা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ভালো গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাস্তবে এসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঠিকঠাক থাকলেও গণতন্ত্রের গুণগত মান শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে রাজনৈতিক আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতির ওপর। এটাই আসল কথা এবং এই সংস্কৃতি একদিনে গড়ে ওঠে না, ধীরে ধীরে তৈরি হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা নিয়ে ‘টুয়েন্টি ইয়ার্স অফ রিফর্মস’ নামে একটি বিখ্যাত বই আছে। বইটি মূলত দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কার নিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা অনেকটা বাংলাদেশের মতোই ছিল—সার্কিট জাজ থেকে শুরু করে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সব জায়গাই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। নিয়ম-নীতির বালাই ছিল না, ছিল মাফিয়া তন্ত্র। মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সেই সংস্কৃতি বদলে আমেরিকা কীভাবে একটি নিয়মবদ্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আসতে পারল, তা লক্ষণীয়। আমরা অতীতে যা দেখেছি, তা বদলাতে হবে। রাজনীতি যদি জনকল্যাণমুখী না হয়ে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা বিতরণের হাতিয়ার হয়—যা আমরা এতদিন দেখে এসেছি—তাহলে যুবসমাজের একটি বড় অংশ ‘ক্যাডার ভিত্তিক’ রাজনীতি বা চাঁদাবাজিকেই জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। শুধু তাই নয়, একটি সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কেবল ব্যবসার পরিবেশই নষ্ট করে না (যাকে আমরা ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’ বলি), বরং তারা অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণকেও নিজেদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসে। এর ফলে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
আমার মনে হয়, একটি বিষয় হয়তো কেউ সেভাবে তুলে ধরেননি—তা হলো আমাদের শিক্ষার নিম্নমান এবং বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়া। এর সঙ্গে যুব বেকারত্ব ও যুবসমাজের একাংশের রাজনৈতিক ক্যাডারভিত্তিক জীবিকার প্রতি ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি পরস্পর সম্পর্কিত। এই সমস্যাগুলোর সমাধান পৃথকভাবে করা সম্ভব নয়। আমরা হয়তো এভাবে বিষয়টি ভেবে দেখিনি। তাই শুধু রাজনীতির ওপর দোষ চাপালেই চলবে না; আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বেকার সমস্যার দিকেও নজর দিতে হবে।
ধরলাম, আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—সেই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে নিশ্চিত হবে? শুধু গণতন্ত্র থাকলেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাছাড়া বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশই বা কীভাবে তৈরি হবে? এটি তো শুধু সরকারের একার বিষয় নয়। বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অনেক আন্তর্জাতিক সূচক রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ সবসময়ই পিছিয়ে। একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়—যদিও আমরা অনেকে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না—যে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা কমালে বা লাইসেন্স পাওয়ার সময় কমিয়ে আনলেই ব্যবসার পরিবেশ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কেবল আমলাতান্ত্রিক সমাধান দিয়ে এই পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।
আমাদের দেশে ব্যবসায়ী এবং আমলা বা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যদি একটি অশুভ লেনদেন বা আঁতাতের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তবে তা কেবল প্রশাসনিক সংস্কার দিয়ে হঠাৎ করে ঠিক করা যায় না। এটি সত্য যে, আমরা নতুন আইন-কানুন ও বিধি-বিধান তৈরি করতে পারি, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং এতে কিছু সমস্যার সমাধানও হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই—এই বছর থেকে—অনলাইনে আয়কর জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছি। এর ফলে কর কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ আর নেই, যা নিঃসন্দেহে সাধারণ করদাতাদের হয়রানি বন্ধ করবে। এটি অবশ্যই কার্যকর একটি পদক্ষেপ। কিন্তু বড় বড় কর ফাঁকির ঘটনাগুলো যে শুধু অনলাইনে কর ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাধান হবে, তা নিশ্চিত নয় বা আমি তা মনেও করি না। সেটির জন্য আরও বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। মোদ্দাকথা হলো, আমরা আইন-কানুন বা বিধি-বিধান দিয়ে যা-ই করতে চাই না কেন, সেটার ফলাফল নির্ভর করবে ওই দেশের তৎকালীন ব্যবসায়িক-আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা আচরণবিধির ওপর—যাকে আমরা বলি ‘সোশ্যাল সুপার স্ট্রাকচার’। আমরা যেসব নতুন বিধি-বিধান দিচ্ছি, সেগুলো কী ধরনের প্রণোদনা বা ইনসেনটিভ তৈরি করছে, তা এই কাঠামোর ওপরই নির্ভর করে। আমি যদি ওই পরিবেশ বা আচরণকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে ভুলভাবে নতুন বিধি-বিধান চাপিয়ে দিই, তবে তার ফলাফল অনির্দিষ্ট হতে পারে। যদি সেটি কার্যকর হয়, তবে হয়তো উৎপাদনশীল উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। কিন্তু কার্যকর না হলে তা উল্টো ‘রেন্ট সিকিং’ বা অবৈধ উপার্জনের দিকেই মানুষকে ঠেলে দেবে। তখন মনে হবে আমরা ভালো বিধি-বিধান করছি, কিন্তু আদতে তা অবৈধ উপার্জনের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে।
আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত সংস্কারের অধীনে বলা হতো—ঢালাওভাবে উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ করে যাও, তাহলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং সব সমস্যার সমাধান মিলবে। কিন্তু ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংক নিজেই একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানায় যে, তাদের এই উদারীকরণ ও সংস্কারের পরামর্শ একেক দেশে একেক রকম ফলাফল দিয়েছে। কোনো দেশে ভালো ফল মিলেছে, আবার কোনো দেশে উল্টো ক্ষতি হয়েছে। এর কারণ হলো, একটি দেশের আচরণবিধি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ ‘রিলেশনশিপ অফ ট্রাস্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন’ কেমন—তার ওপর বিষয়টি নির্ভর করে। একে ‘সোশ্যাল ক্যাপিটাল’ বা সামাজিক মূলধনও বলা হয়। আমরা যখন নতুন বিধি-বিধান চাপিয়ে দিই, তখন সেটির কার্যকারিতা কতটুকু হবে, তা মূলত এই সামাজিক মূলধনের ওপরই নির্ভর করে।
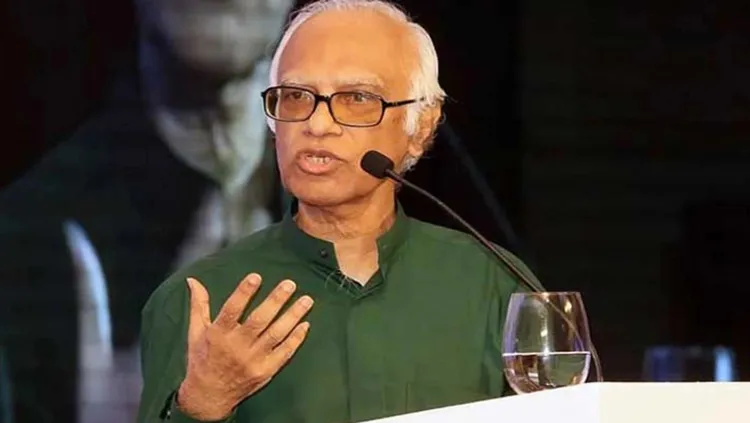
আমি দু-একটি উদাহরণ দিতে চাই। আগেই বলেছি, নতুন করে ভাবার সময় আমি পাইনি, তবে কিছু উদাহরণ আমি লক্ষ্য করেছি। যেমন—ভারতে ঘুষ নেওয়া যেমন ফৌজদারি অপরাধ (ক্রিমিনাল অফেন্স), তেমনি ঘুষ দেওয়াও অপরাধ। আমাদের অনেকের পরিচিত কৌশিক বসু, যিনি একসময় ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ঘুষ দেওয়াও যদি অপরাধ হয়, তবে কেউ আর ‘হুইসেল ব্লোয়ার’ হবে না। অর্থাৎ, কেউ নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলবে না যে—অমুক কর্মচারী আমার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ঘুষ দেওয়াকে যেন অপরাধ হিসেবে গণ্য না করা হয়। কিন্তু তখন ভারতের গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজে এ নিয়ে তুমুল হইচই পড়ে যায়। তারা মনে করেছিলেন, এটি একটি অনৈতিক প্রস্তাব যা ঘুষ দেওয়াকে বৈধতা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।
বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখলাম, বাংলাদেশে ঘুষ নেওয়া অপরাধ হলেও ঘুষ দেওয়াকে সবসময় সেভাবে অপরাধ হিসেবে দেখা হয় না। কিন্তু তারপরও তো খুব একটা লাভ হয়নি। এর কারণ হলো, যখন কোনো অবৈধ সুবিধা আদায়ের জন্য—যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য—ঘুষ দেওয়া হয়, তখন যিনি দিচ্ছেন তিনিও বিষয়টি প্রকাশ করবেন না। বাংলাদেশ বা আমাদের মতো দেশগুলোতে অনেক ঘুষ লেনদেন হয় ‘স্পিড মানি’ হিসেবে। এতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ থাকে, তাই কেউই এ নিয়ে কথা বলে না।
আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘সরকারি ক্রয় নীতি সংশোধন ২০২৫’ পাস হয়েছে এবং এটি এখনই কার্যকর। সরকারি ব্যয়ের বিশাল অংশ—উন্নয়ন বাজেট, পরিচালন বাজেট, রাজস্ব বাজেট—সবকিছুই এই ক্রয় নীতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা একদম উপজেলা পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য হলো ঠিকাদারি খাতের একচেটিয়া প্রভাব ভাঙা। আমরা দেখেছি, রেলওয়ে বা সড়ক ও জনপথের মতো বিভিন্ন খাতে দু-তিনটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বা একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে কাজগুলো কুক্ষিগত করে রেখেছে। নতুন নীতিমালার অধীনে টেন্ডার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ওই সেক্টরের অতীত অভিজ্ঞতাই এখন আর মূল্যায়নের একমাত্র মাপকাঠি নয়। বেনামে ঠিকাদারি নেওয়ার কোনো সুযোগ আর থাকছে না; অর্থাৎ প্রভাব খাটিয়ে কাজ নিয়ে অন্যকে দিয়ে করানো যাবে না। এতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। যারা হয়তো আগে কখনো টেন্ডারে অংশ নেয়নি কিন্তু ভালো ব্যবসায়ী, যাদের কর ও ব্যবসার নথিপত্র স্বচ্ছ—তাদের এখন পার্টনার হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।
যাইহোক, এগুলো আমার মূল কথা নয়। আমি আসলে যেটা বলতে চেয়েছি তা হলো, টেন্ডারের মূল্যায়ন পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। কোনো একটি দেশে টেন্ডার মূল্যায়নের আদর্শ পদ্ধতি কী হবে, তার কোনো ধরাবাঁধা ফর্মুলা নেই। এটি মূলত নির্ভর করে যে সরকারি কর্তৃপক্ষ টেন্ডার আহ্বান করছে এবং যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আবেদন করছে—এই দুই পক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। বিভিন্ন দেশে এই পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। যদি উভয় পক্ষকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হয়—আমাদের ক্ষেত্রে যা দিয়েই শুরু করতে হচ্ছে, যেখানে টেন্ডার আহ্বানকারী কর্মকর্তাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন এবং ঠিকাদার যে কুকর্ম করবেন না তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই—সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতিকে একদম নিয়মবদ্ধ করে দিতে হয়। সেখানে কোনো ‘ডিসক্রিপশন’ বা নমনীয় মূল্যায়নের সুযোগ রাখা যায় না।
তবে এর একটি নেতিবাচক দিকও আছে। যদি আমি কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হতাম, তবে আমি নমনীয়ভাবে চাইতাম যেন সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই কাজটা পায়; কেবল নিয়ম-নীতির ফর্মুলার মধ্যে আটকে না থেকে নিজের বিবেচনা ব্যবহার করতাম। কিন্তু এখানেই একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়—একদিকে কীভাবে দুর্নীতির সুযোগ কমানো যাবে, আর অন্যদিকে কীভাবে প্রকৃত ভালো দরদাতা বাছাই করা যাবে। আমি এ কথাটি বললাম কারণ, এই ফর্মুলাটি কী হবে তা নির্ভর করে ওই দেশে এই দুই পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার সংস্কৃতি কতটা গড়ে উঠেছে তার ওপর। হয়তো ভবিষ্যতে এই ফর্মুলা বদলানো যাবে বা আরও নমনীয় করা যাবে, যখন আমরা দেখব যে সত্যিই ভালো ভালো ঠিকাদার এসেছে, তাদের বিশ্বাস করা যায় এবং কর্তৃপক্ষও আরও সৎ হয়েছে।
আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সেটি হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উৎপাদিত পরিসংখ্যান, বিশেষ করে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হিসাব। এসব পরিসংখ্যান বিবিএস নিজেরা সরাসরি প্রকাশ করে না; সরকারের মন্ত্রীকে তা অনুমোদন করতে হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সন্দেহ তৈরি হয়েছে। একটি হলো বিবিএস-এর সক্ষমতার বিষয়। যেকোনো উন্নয়নশীল দেশে তারা যেসব পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে, সেগুলোর মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকে এবং গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থাকে। আরেকটি হলো, সরকার প্রভাব বিস্তার করে মূল্যস্ফীতি কম দেখাতে চাচ্ছে কি না, কিংবা জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেখাতে চাচ্ছে কি না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এমনটা প্রায়ই ঘটে। আসলে জিডিপি বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি খুব ভালো একটি সূচক নয়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ভালো হলেই যে সবার কল্যাণ সাধিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। ১৯৩০-এর দশকে বা ৪০-এর দশকের শুরুতে যখন সাইমন কুজনেট জিডিপি ধারণাটি তৈরি করেন, তখন তা মূলত যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমরাস্ত্র সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ তৈরির জন্য করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ৫০-এর দশকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্সের রিচার্ড স্টোন এবং কেইনসের ছাত্ররা মিলে ‘ইনপুট-আউটপুট টেবিল’ ব্যবহার করে জিডিপিকে আজকের কাঠামোতে রূপ দেন।
যাই হোক, আমি বলছিলাম যে বিবিএস-এর সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং আমরা তা নিয়ে ভাবছি। হোসেন জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠেছে—বিবিএসকে স্বাধীন করে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? স্বাধীন করলেও তো যেকোনো প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত সরকারের অধীনেই থাকে এবং সক্ষমতার বিষয়টিও থেকে যায়। তার চেয়েও বড় কথা—আমার নিজের বিশ্বাস, এবং এ কারণেই কিছু বিধি-বিধান ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং পরিসংখ্যান আইনে নতুন ধারা সংযুক্ত করার উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি—তা হলো বিবিএস-এর স্বাধীনতার চেয়েও বেশি জরুরি হলো তাদের উৎপাদিত পরিসংখ্যান ও তথ্যের স্বচ্ছতা।
জিডিপির প্রবৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করতে অসংখ্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই ব্যক্তিগত তথ্য নয়; এগুলো অন্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তিগত কোনো পরিসংখ্যান হলে আন্তর্জাতিক প্রোটোকল অনুযায়ী ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হয়। যেমন—সার্ভে বা জরিপ প্রকাশ করার সময় ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে যেন চেনা না যায়, তা নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু জিডিপি বা মূল্যস্ফীতির হিসাব তো আসে অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, যেখানে গোপনীয়তার কোনো অবকাশ নেই। কাজেই জিডিপি কীভাবে মাপা হচ্ছে, প্রবৃদ্ধি বা মূল্যস্ফীতি কীভাবে প্রতি বছর হিসাব করা হচ্ছে, কোন বাজারের কোন জায়গা থেকে কোন সামগ্রীর দাম প্রতি সপ্তাহে নেওয়া হচ্ছে—এসবের মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই। আমার সামনে সাংবাদিক রিজভী বসে আছেন; আমি তাঁকেই বলছি—আপনি যদি সন্দেহ করেন যে মূল্যস্ফীতি কম দেখানো হচ্ছে অথচ বাজারে দাম বেশি, তবে বিবিএস-এ যান। আমি এখনই বিষয়টিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আপনারা যাচাই করুন—আলু বা পেঁয়াজের দাম ঠিক কোন কোন বাজার থেকে নেওয়া হয়েছে। যদি মনে হয় সেটা বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না, তাহলে প্রশ্ন তুলুন যে এটা ঠিক হয়নি। এই স্বচ্ছতাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার।
এই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়তো এখন একটু কঠিন, তবে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানকেই ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। বিবিএসকেও সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। একবার ডিজিটালাইজড হয়ে গেলে এই তথ্যের প্যাকেজগুলো যেকোনো গবেষক বা সাংবাদিক চাইলেই নিতে পারবেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন। এতে সুবিধা হবে এই যে, গবেষকরা পরামর্শ দিতে পারবেন—'এই পরিমাপের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো একটি পরিসংখ্যানের উৎস ছিল, সেটি ব্যবহার করলে ফল আরও নির্ভুল হতো।' ফলে বিবিএস-এর তথ্য ভাণ্ডারও আরও সমৃদ্ধ হবে।

সংস্কারের এই বিষয়গুলো বললাম, যাকে প্রাতিষ্ঠানিক বা আমলাতান্ত্রিক সংস্কার বলা যায়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, অবৈধ আয় বা ‘রেন্ট সিকিং’ কমাতে গেলে তা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, যদি অবৈধ আয়ের উপার্জনের একটি রাজনৈতিক চাহিদা থাকে, তবে শুধু নতুন আইন বা বিধি-বিধান দিয়ে তা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা যায় না। আমি যদি আয়ের একটি অবৈধ উৎস বন্ধ করে দিই, তবে অন্য আরেকটি উৎস খুঁজে বের করা হবে। অতীতে আমরা ঠিক এমনটাই ঘটতে দেখেছি।
যেকোনো রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থাতেই উন্নয়নের অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সফল ও ব্যর্থ—উভয় ধরনের উন্নয়নের দৃষ্টান্তই রয়েছে। সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হোক, একনায়কতান্ত্রিক হোক, স্বৈরশাসন হোক, কিংবা মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দীর্ঘদিনের একদলীয় প্রাধান্যের শাসন হোক—সব ধরনের শাসনব্যবস্থাতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভালো হতে পারে। শুধু গণতন্ত্রই যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক, বিষয়টি তা নয়। বরং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি—দুই-তিন দশক ধরে ক্রমাগতভাবে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের ওপরে থাকা। যেমনটা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এবং ইস্ট এশিয়ান মিরাকল ইকোনমিগুলোতে হয়েছিল। বর্তমানে চীনে যা হচ্ছে, ভিয়েতনামে কিছুটা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ায় নতুন করে যুক্ত হচ্ছে এবং মালয়েশিয়ায় অনেক আগেই সেই উত্তরণ ঘটেছে।
এই সবগুলো দেশের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমি আমার বইতে প্রথম উল্লেখ করেছিলাম। সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি হলো ‘অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেকানিজম ইন দ্য গভর্নেন্স সিস্টেম’ বা শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার কাঠামো। প্রশাসন যন্ত্রের সকল পর্যায়ে একটি শক্ত জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার বিষয়টি তো আমরা জানিই—সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ওয়াচডগ প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত সংসদ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কিন্তু আমরা অনেক সময় যা লক্ষ্য করি না তা হলো—চীনে ১৯৮০-র দশকে যখন বাজারমুখী সংস্কার শুরু হলো, তখন সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির একদলীয় শাসন থাকা সত্ত্বেও দলের ভেতরেই একটি বড় ধরনের সংস্কার করা হয়েছিল। সেটি হলো—প্রত্যেকটি স্তরে যারা অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের সময়ভিত্তিক ও ফলাফলভিত্তিক প্রতিটি নীতির সফলতা নিয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। নিয়মটা ছিল এমন—তুমি নীতি নির্ধারণ করো, সফল হও, তাহলে ভালো ফল পাবে; আর বিফল হলে চাকরিচ্যুত হবে। ভিয়েতনামেও ১৯৯০-এর দশকে যখন বাজার অর্থনীতি নীতি চালু হলো, তখন তারাও তাদের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে এই ধরনের সংস্কার এনেছিল।
এই প্রসঙ্গে আমি এটাও বলব যে, একটি দেশের আচরণবিধি, মূল্যবোধ এবং একে অপরের প্রতি আস্থা ও সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে উদারীকরণ কতদূর সফল হবে। ভিয়েতনামের বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই আশ্চর্যজনক। যখন তারা প্রথম বাজার অর্থনীতির উদারীকরণ করে, তখন তারা ভাবেনি যে এর জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো লাগবে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা একচেটিয়া ব্যবসা থামানোর জন্য আইন করতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভিয়েতনামের ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নিজেরাই একত্রে বসে ঠিক করলেন যে, তারা কীভাবে নিয়মের ভেতর চলবেন। তারা স্থির করলেন যে, কেউ একে অপরের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় যাবেন না, মূল্যহার প্রতিযোগিতামূলক রাখবেন এবং ঋণ নিলে তা ফেরত দেবেন। এটি সম্পূর্ণই একটি সাংস্কৃতিক বিষয়।
আমি যখন এই জবাবদিহিতা বা ‘অ্যাকাউন্টেবিলিটি’ নিয়ে কথা বলেছিলাম—অনেকের হয়তো মনে আছে, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরেও আমি বলেছিলাম যে, সফল দেশে সকল স্তরের প্রশাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতাই মূল বিষয়। তখন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন একটি বিষয় যোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জবাবদিহিতাই সব নয়, এর সঙ্গে দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। জবাবদিহিতা বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি হলো একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আর দায়িত্ববোধ বা ‘সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি’ হলো একটি নৈতিক আচরণের বিষয়।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগের কালের একজন মফস্বলের এলএমএফ পাস করা ডাক্তার—তিনি ঠিক সময়ে অফিসে আসছেন কি না বা রোগী দেখছেন কি না, সেটা হলো তাঁর জবাবদিহিতা। কিন্তু তিনি যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের খোঁজ নেন, কোনো গরিব রোগী খুব অসুস্থ হলে তাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন—সেটা তো জবাবদিহিতা নয়, সেটা হলো দায়িত্ববোধ। প্রাইমারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তাই। এখনকার অনেক প্রাইমারি শিক্ষক ছাত্রদের জিম্মি করে পরীক্ষা বন্ধ রেখে স্ট্রাইকে যাচ্ছেন। অথচ আমার ছোটবেলায় প্রাথমিক শিক্ষকরা আমার বাসায় এসে খোঁজ নিতেন যে, আমার অঙ্কে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না বা ইংরেজিতে কোনো অসুবিধা আছে কি না। এটাই হলো দায়িত্ববোধ।
আমি তৃতীয় যে বিষয়টি বলেছিলাম—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতিতে কীভাবে একটি ন্যায্য সমাজ এবং বৈষম্য নিরোধক উন্নয়ন সম্ভব হবে? বর্তমানে আমরা জুলাই সনদ বা ঐক্যমত কমিশন নিয়ে যেসব আলোচনা করছি, সেখানে এই বিষয়গুলো নেই। এটা স্বাভাবিক, কারণ এই বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয়। এখানে নীতি নির্ধারণের অনেক বিষয় আছে। এখানেই বাম, ডান, মধ্য-ডান বা মধ্য-বাম—এ ধরনের আদর্শগত দলের পার্থক্য তৈরি হয়। তাই নীতির ব্যাপারে এখানে ঐকমত্য হবে না, এবং সে কারণেই এটি এখন আলোচিত হচ্ছে না। তবে আমরা আশা করব, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এবার আসা যাক ‘ন্যায্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা’ ঠিক কি সেই আলোচনায়। আসলে এখানে ন্যয্যতার সংজ্ঞাটি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। শুধু ‘ন্যায্য অর্থনীতি’ বা ‘বৈষম্যহীন অর্থনীতি’ বললেই বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। কী ধরনের বৈষম্যহীনতা? এর সংজ্ঞা নিয়ে দার্শনিকরাও দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করেও কোনো একক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।
সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচিগুলোর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কীভাবে হবে? শুধু সুরক্ষা দেব বা দারিদ্র্য কমে যাবে বললেই তো হবে না। এই সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারের যে আয়ের প্রয়োজন, তা কোথা থেকে আসবে বা কী কর-নীতির মাধ্যমে আসবে? আয় পুনর্বণ্টন করতে হলে কর ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত? বাজার ও রাষ্ট্রের সম্পর্কই বা কী রকম হবে, যাতে একচেটিয়া ব্যবসা তৈরি না হয় এবং মুনাফা-তাড়িত ব্যবসাকে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা যায়? উদ্যোক্তাদের জন্য সমান সুযোগ কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে? কয়েকজন বড় বড় শিল্পপতি যেন পুরো নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়াকে কুক্ষিগত করতে না পারেন, তার ব্যবস্থা কী হবে? সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কীভাবে ক্ষমতায়িত করা যাবে?

এছাড়া পরিবেশের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে—আমাদের মতো দেশে এটিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আমরা যখন কোনো ‘কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস’ (ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ) করি, তখন একটি ‘ডিসকাউন্ট রেট’ ধরি এবং সাধারণত ৩০ বছরের মেয়াদে সেই হিসাব করি। আজকের ১০ টাকার ক্ষতি এবং ৩০ বছর পরের ১০ টাকার ক্ষতিকে আমরা এক করে দেখি না; ভবিষ্যতের ক্ষতিকে আমরা অনেক কম গুরুত্ব দিই। আমার জীবদ্দশায় বা একটি প্রজন্মের জীবদ্দশায় আমি ভবিষ্যৎকে কম গুরুত্ব দিতেই পারি। কিন্তু আমরা যখন পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করছি, তখন আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবছি। পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থকে ‘ডিসকাউন্ট’ করার বা খাটো করে দেখার নৈতিক অধিকার আমাকে কে দিল? আমার কাছে যদি পরিবেশের ক্ষতি ১০ টাকা হয়, তবে আমার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কেন তা ১০ টাকার চেয়ে কম হবে? এটি অর্থনীতিবিদদের কাছেও একটি বিরাট প্রশ্ন, যার সমাধান এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও এ বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন গবেষক উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা পরিবেশবাদীরা গ্রহণ করেননি।
আমার বই দুটোতে মূলত এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো, এগুলো নিয়ে বিশদ কথা বলার সময়ও এখন নেই। তাছাড়া এই বইগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আমার দল-নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হতে পারে এবং আমার আদর্শগত অবস্থান প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। বর্তমান সময়ে ‘ট্যাগিং’ বা তকমা দেওয়ার যে প্রবণতা চলছে, তাতে বিষয়টি বেশ বিপদজনক।
তবে আমি দুটি সাধারণ বা মৌলিক প্রতিপাদ্য দিয়ে শেষ করতে চাই, যা আমার সহকর্মী গবেষকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আশা করি: এক. কোনো দেশই এত দরিদ্র নয় যে তার সকল নাগরিকের ন্যূনতম জীবিকা ধারণের চাহিদা মেটাতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন কেবল উপযুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা। দুই. লর্ড মেইনার্ড কেইনস সুশাসনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাংক অনেক পরে এসে আমাদের সুশাসন শেখাতে গেছে, কিন্তু তার বহু আগে ১৯৩০-এর দশকে কেইনস বলেছিলেন—সুশাসন হলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় বা ভারসাম্য রক্ষা করা। এর থেকে একটি অনুসিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে। যদিও অর্থনীতিবিদরা আয় বণ্টনের অনেক বিকল্প তত্ত্ব দিয়ে থাকেন—যাকে নিও-ক্লাসিক্যাল, কেইনসিয়ান বা ক্যালেস্কিয়ান তত্ত্ব বলা হয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আয় বণ্টন কীভাবে নির্ধারিত হবে, তা হয়তো নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর। এটি আমার কথা নয়; ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি বলেছেন। যিনি ‘ক্যাপিটাল ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি’ লিখেছেন। পিকেটি বলেছিলেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো বৈষম্য বাড়িয়ে দেওয়া। ২০১৫ সালের দিকে প্রকাশিত তাঁর ‘দ্য ইকোনমিকস অফ ইনইকুয়ালিটি’ বইয়ে তিনি বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আয় বণ্টনের যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উত্থানের সম্পর্ক অত্যন্ত জোরালো।
পরিশেষে, আজকের এই আয়োজনের জন্য বিআইডিএসকে ধন্যবাদ জানাই। যারা এখানে যোগ দিয়েছেন—সংবাদকর্মী, অংশগ্রহণকারী এবং যারা প্রবন্ধ পাঠ করবেন—সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি।
লেখক: অর্থনীতিবিদ ও অন্তর্বর্তী সরকারের পরিকল্পনা উপদেষ্টা
৭ ডিসেম্বর বিআইডিএসের বার্ষিক উন্নয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের ভিত্তিতে প্রণীত। অনুলিখন: মুজাহিদুল ইসলাম

দীর্ঘ অচলায়তন ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর অবশেষে অনুষ্ঠিত হলো দেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নানা সংকট, মতবিরোধ ও আস্থাহীনতার আবহ পেরিয়ে এই নির্বাচন ছিল রাষ্ট্র ও রাজনীতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের মুহূর্ত।
১২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে সরকার গঠন করতে চলেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন নিয়ে এই জয় যেমন বিপুল প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে, তেমনই তৈরি করেছে এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি।
১ দিন আগে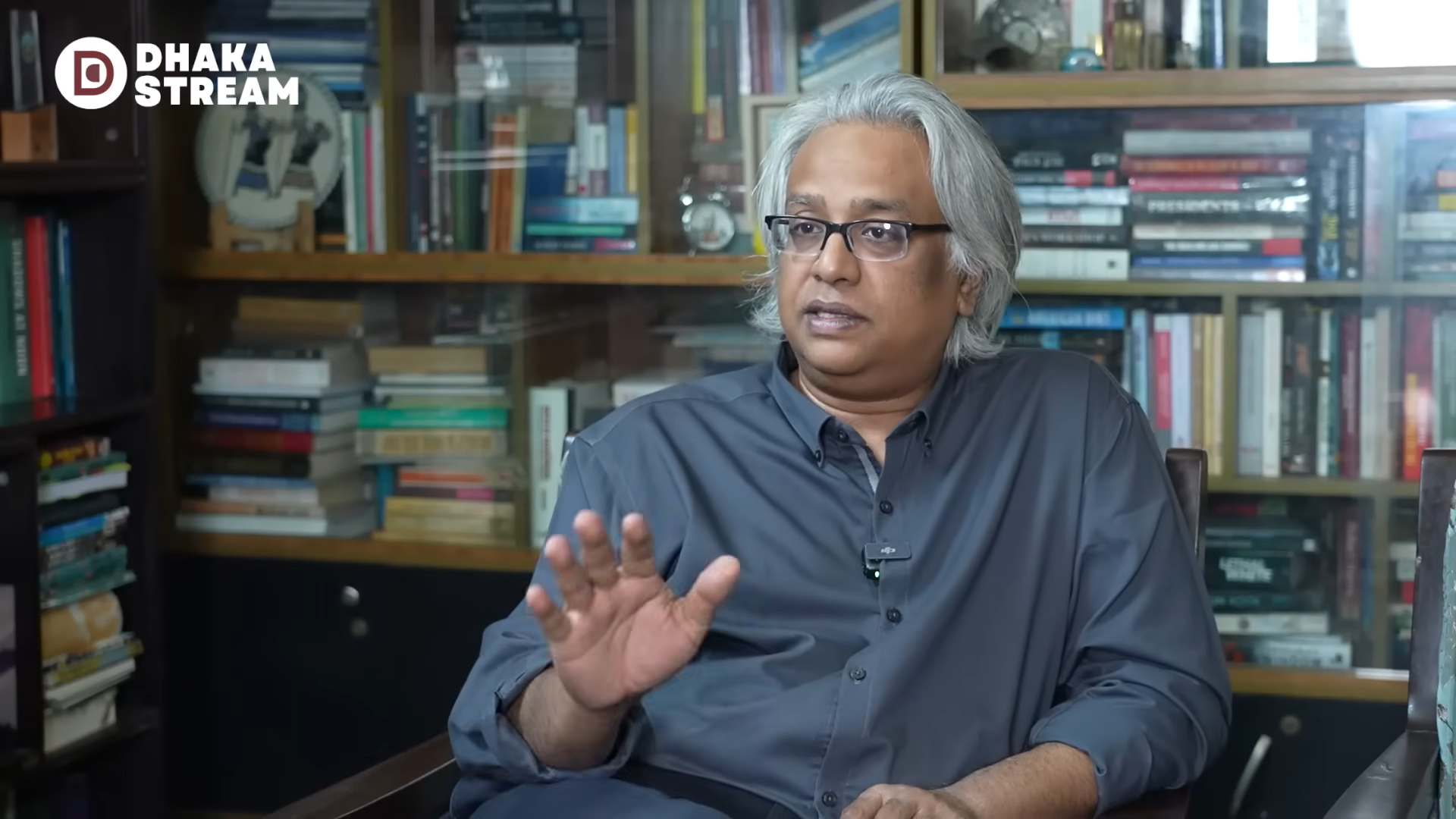
এখন মানুষের প্রত্যাশা বা এক্সপেকটেশন অনেক বেশি। এই সরকারের কাছে মানুষ অনেক কিছু আশা করবে। আর এখানেই বিপদ। সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা এই প্রত্যাশাগুলো শুনতে পাচ্ছে এবং তাদের কাজে তার প্রতিফলন আছে। অতিরিক্ত প্রত্যাশার বিপদ হলো, আপনি যখন ডেলিভার করতে পারবেন না, তখন জনপ্রিয়তা খুব দ্রুত পড়ে যায়।
২ দিন আগে
ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন তৈরি করা গেলে কৃষক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সরাসরি সংযোগ স্থাপন সম্ভব হবে। যদি সরকার শুরুতেই এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে।
২ দিন আগে