.png)
প্রতি কেজি এলপিজি গ্যাসের দাম ১১৬ টাকা ৯৪ পয়সা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১১৩ টাকা ৬৪ পয়সায়। যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও প্রতি লিটার ৬৪ টাকা ৩০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৬২ টাকা ৪৬ পয়সা করা হয়েছে। তবে সরকারি খাতের সরবরাহে ব্যবহৃত সাড়ে ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম আগের মতোই ৮২৫ টাকা।

স্ট্রিম প্রতিবেদক
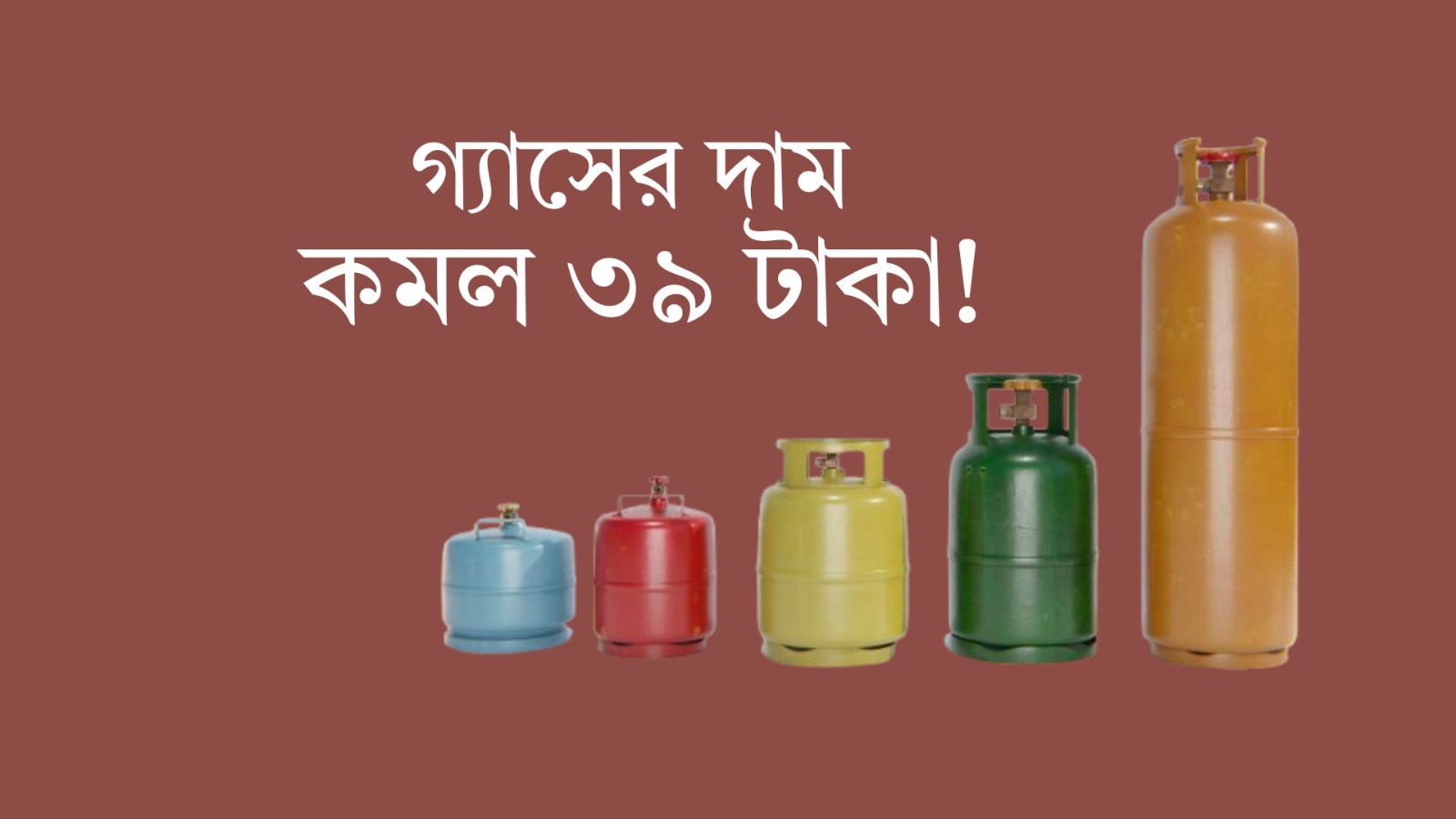
চলতি জুলাই মাসে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম কিছুটা কমেছে। সারা বছরই ওঠানামা করে এলপিজির দাম। গত মাসেও ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম ছিল ১ হাজার ৪০৩ টাকা, এ মাসে তা কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৬৪ টাকা। ফলে প্রতিটি সিলিন্ডারে ৩৯ টাকা কমেছে। কিন্তু এই দাম কেন বাড়ে-কমে, এর সুবিধাই বা কতটা পান ভোক্তারা?
গত বুধবার (২ জুলাই) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কেজিতে এলপিজির দাম কমেছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। ফলে প্রতি কেজি এলপিজি গ্যাসের দাম ১১৬ টাকা ৯৪ পয়সা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১১৩ টাকা ৬৪ পয়সায়। যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও প্রতি লিটার ৬৪ টাকা ৩০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৬২ টাকা ৪৬ পয়সা করা হয়েছে। তবে সরকারি খাতের সরবরাহে ব্যবহৃত সাড়ে ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম আগের মতোই ৮২৫ টাকা রাখা হয়েছে।
প্রতি মাসে এলপিজির দাম পরিবর্তন পেছনের অন্যতম কারণ হলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রোপেন ও বিউটেন-এর দামের ওঠানামা। বাংলাদেশ এলপিজি উৎপাদন করে না, আমদানি করতে হয়। আর আন্তর্জাতিক বাজারে সৌদি আরবভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আরামকো প্রতিমাসে ‘সৌদি কার্গো প্রাইস’ (সিপি) প্রকাশ করে। এই প্রকাশিত দামের সঙ্গে সমন্বয় করেই বাংলাদেশে দাম নির্ধারিত হয়।
বিইআরসির সচিব মো. নজরুল ইসলাম সরকার জানান, আমাদের দেশে গ্যাসের দাম ওঠানামা করার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। সৌদি আরবে দামের পরিবর্তন এবং ডলারের দাম ওঠানামা।

প্রতিষ্ঠানটির গ্যাস সেক্টরের পরিচালক প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘গ্যাসের দাম নিয়মিতই ওঠানামা করে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এর পার্থক্য সাধারণত বেশি হয় না। আবার যুদ্ধ বা কোনো আন্তর্জাতিক সংকট হলে ভিন্ন কথা। যেমন হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে আমরা আর গ্যাসই পেতাম না।’
মো. হেলাল উদ্দিন আরও বলেন, ‘আমাদের আমদানি-নির্ভরতা কমাতে হবে। বিগত সময়ে বাংলাদেশের গ্যাস অনুসন্ধান না করে শুধু আমদানিই করা হয়েছে।’
কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) করা একটি মামলার পর ২০২০ সাল থেকে এলপিজির দাম নির্ধারণ শুরু হয়। এরপর থেকে গণশুনানির আয়োজন করে আসছে বিইআরসি। যেখানে এলপিজি আমদানিকারক ও বিতরণকারী কোম্পানি এবং ভোক্তাপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শুনানিতে সকল পক্ষের যুক্তি-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
শুনানির ভিত্তিতে বিইআরসি নিয়মিত দাম সমন্বয় করলেও বাজারে তার বাস্তব প্রতিফলন সব সময় পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে অনেক সময় ভোক্তারা এর পুরোপুরি সুফল পান না।
এ বিষয়ে কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক শামসুল আলম স্ট্রিমকে বলেন, ‘মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের আইন এটার জন্য দায়ী। এ ছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের আইনে সীমাবদ্ধতা আছে। আবার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশের যে আইনি কাঠামো আছে, তা ব্যবহার করার সক্ষমতা ভোক্তাদের নেই।’
সরকার নিয়ম করলেও সেটার সুফল পাচ্ছে না ভোক্তারা। খুচরা পর্যায়ে দাম কমার প্রভাব কমই পড়ে। এসব ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সুফল ‘আদায়’ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে অধ্যাপক শামসুল আলম আরও বলেন, ‘বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে, তাতে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন এসেছে। এটা সর্বজনীন হলে এ অবস্থার পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সেই সুযোগ কম। কারণ, এই অবস্থা গোষ্ঠীগত, দলগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ভোক্তাদের সুফল আদায় করে নিতে হবে। যেমন সংবিধান ও আইনে পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু জ্বালানি ক্ষেত্রে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয়নি।’
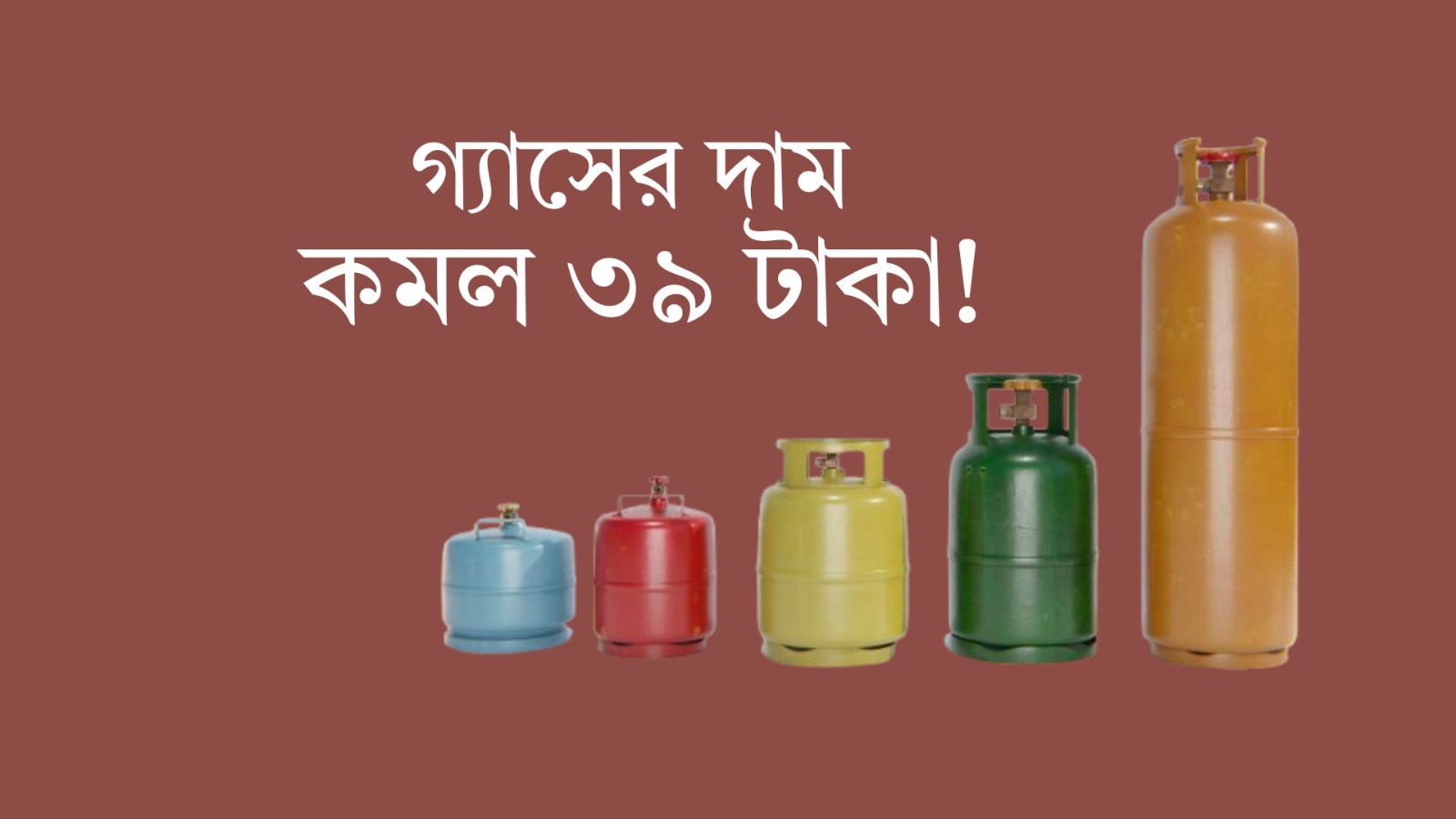
চলতি জুলাই মাসে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম কিছুটা কমেছে। সারা বছরই ওঠানামা করে এলপিজির দাম। গত মাসেও ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম ছিল ১ হাজার ৪০৩ টাকা, এ মাসে তা কমে হয়েছে ১ হাজার ৩৬৪ টাকা। ফলে প্রতিটি সিলিন্ডারে ৩৯ টাকা কমেছে। কিন্তু এই দাম কেন বাড়ে-কমে, এর সুবিধাই বা কতটা পান ভোক্তারা?
গত বুধবার (২ জুলাই) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কেজিতে এলপিজির দাম কমেছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। ফলে প্রতি কেজি এলপিজি গ্যাসের দাম ১১৬ টাকা ৯৪ পয়সা থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১১৩ টাকা ৬৪ পয়সায়। যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাসের দামও প্রতি লিটার ৬৪ টাকা ৩০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৬২ টাকা ৪৬ পয়সা করা হয়েছে। তবে সরকারি খাতের সরবরাহে ব্যবহৃত সাড়ে ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম আগের মতোই ৮২৫ টাকা রাখা হয়েছে।
প্রতি মাসে এলপিজির দাম পরিবর্তন পেছনের অন্যতম কারণ হলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রোপেন ও বিউটেন-এর দামের ওঠানামা। বাংলাদেশ এলপিজি উৎপাদন করে না, আমদানি করতে হয়। আর আন্তর্জাতিক বাজারে সৌদি আরবভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আরামকো প্রতিমাসে ‘সৌদি কার্গো প্রাইস’ (সিপি) প্রকাশ করে। এই প্রকাশিত দামের সঙ্গে সমন্বয় করেই বাংলাদেশে দাম নির্ধারিত হয়।
বিইআরসির সচিব মো. নজরুল ইসলাম সরকার জানান, আমাদের দেশে গ্যাসের দাম ওঠানামা করার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। সৌদি আরবে দামের পরিবর্তন এবং ডলারের দাম ওঠানামা।

প্রতিষ্ঠানটির গ্যাস সেক্টরের পরিচালক প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘গ্যাসের দাম নিয়মিতই ওঠানামা করে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এর পার্থক্য সাধারণত বেশি হয় না। আবার যুদ্ধ বা কোনো আন্তর্জাতিক সংকট হলে ভিন্ন কথা। যেমন হরমুজ প্রণালি বন্ধ হলে আমরা আর গ্যাসই পেতাম না।’
মো. হেলাল উদ্দিন আরও বলেন, ‘আমাদের আমদানি-নির্ভরতা কমাতে হবে। বিগত সময়ে বাংলাদেশের গ্যাস অনুসন্ধান না করে শুধু আমদানিই করা হয়েছে।’
কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) করা একটি মামলার পর ২০২০ সাল থেকে এলপিজির দাম নির্ধারণ শুরু হয়। এরপর থেকে গণশুনানির আয়োজন করে আসছে বিইআরসি। যেখানে এলপিজি আমদানিকারক ও বিতরণকারী কোম্পানি এবং ভোক্তাপক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শুনানিতে সকল পক্ষের যুক্তি-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
শুনানির ভিত্তিতে বিইআরসি নিয়মিত দাম সমন্বয় করলেও বাজারে তার বাস্তব প্রতিফলন সব সময় পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে অনেক সময় ভোক্তারা এর পুরোপুরি সুফল পান না।
এ বিষয়ে কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক শামসুল আলম স্ট্রিমকে বলেন, ‘মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের আইন এটার জন্য দায়ী। এ ছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের আইনে সীমাবদ্ধতা আছে। আবার জ্বালানি অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশের যে আইনি কাঠামো আছে, তা ব্যবহার করার সক্ষমতা ভোক্তাদের নেই।’
সরকার নিয়ম করলেও সেটার সুফল পাচ্ছে না ভোক্তারা। খুচরা পর্যায়ে দাম কমার প্রভাব কমই পড়ে। এসব ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সুফল ‘আদায়’ করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে অধ্যাপক শামসুল আলম আরও বলেন, ‘বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছে, তাতে কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন এসেছে। এটা সর্বজনীন হলে এ অবস্থার পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সেই সুযোগ কম। কারণ, এই অবস্থা গোষ্ঠীগত, দলগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ভোক্তাদের সুফল আদায় করে নিতে হবে। যেমন সংবিধান ও আইনে পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু জ্বালানি ক্ষেত্রে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয়নি।’

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ভিয়েতনাম-যুক্তরাষ্ট্র নতুন বাণিজ্য চুক্তি ভিয়েতনামের জন্য সুবিধা নিয়ে এলেও বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে।
৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্লেষকেরা বলছেন, আগ্রাসী শুল্কনীতি ও ‘একঘরে’ পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশ্বব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা, ডলারের মানের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে ‘ভূমিকম্পের মতো ঘটনা’।
২ দিন আগে
একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কনীতির শঙ্কা, অন্যদিকে স্বৈরাচার পতনের পর সৃষ্ট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে দেশের পোশাক খাত ও সামগ্রিক অর্থনীতি পড়েছে গভীর উদ্বেগের মুখে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ৩৭ শতাংশ শুল্ক সাময়িকভাবে স্থগিত থাকলেও, সেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন লাখ লাখ পোশাক শ্রমিক।
০৮ জুন ২০২৫